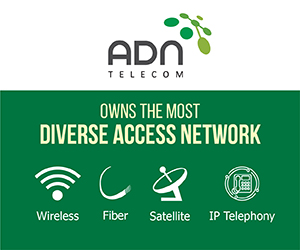সময়টা ১৯৪৫ সালের মে মাস। ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সোভিয়েত শক্তি বার্লিন শহরের রাস্তায় পৌঁছে যায়। রেড আর্মি নাৎসি জার্মানিকে পরাজিত করার জন্য মিত্র শক্তির অংশ হিসেবে লড়াই করে বার্লিনে প্রবেশ করে।
ওই ঘটনার প্রায় ৮০ বছর পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি মস্কোকে আবার পশ্চিম দিকে তার প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দিতে পারে।
কীভাবে এমন ঘটতে পারে?
ঘটনাটি হতে পারে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে কোনও এক ধরনের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে, যা যুক্তরাষ্ট্রের চাপের ফলে হতে পারে। এই চুক্তি অস্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে রাশিয়ার আগ্রাসনের পুরস্কারস্বরূপ কাজ করবে। এতে ভবিষ্যতে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে। বিশেষ করে মস্কো যদি আবার তার সামরিক শক্তি পুনর্গঠন করতে পারে।
রাশিয়ার ট্যাংক পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা যদিও কম। তবু মস্কো ইতোমধ্যেই সীমান্ত পেরিয়ে গুপ্তহত্যা, সাইবার হামলা, নাশকতা এবং অন্যান্য সহিংস কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ না হলেও উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। ফলে সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ার শঙ্কা রয়েছে।
আরও খারাপ হলো, ভবিষ্যতে রাশিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে তা পশ্চিম ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় নয়, বরং সরাসরি সংঘাতের মধ্য দিয়ে ঘটবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে নিজেদের সম্পৃক্ততা কমিয়ে নিলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।
এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অবসানে যেকোনো চুক্তির সুনির্দিষ্ট শর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা সে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হোক বা স্থায়ী শান্তি চুক্তি— এর প্রতিটি দিক গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
দুঃখজনকভাবে ইউক্রেনের জন্য সবচেয়ে ভালো চুক্তির সম্ভাবনা এখন আর নেই। ন্যাটো সদস্যপদ এখনও বহু দূরের স্বপ্ন। এই সদস্যপদ যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারত, তার কোনও সহজ বিকল্প নেই।
তবে এখনও “সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও অপেক্ষাকৃত ভালো” বিকল্প রয়েছে। এটি এমন একটি চুক্তি যা অন্তত রাশিয়ার ইউক্রেনের সীমানা পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে।
এই বিকল্পটি কার্যকর হবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করছে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর। তারা এই তুলনামূলকভাবে ভালো পথে যাবে, নাকি এমন এক পথ বেছে নেবে যার ফলাফল ইউরোপ ও বৈশ্বিক শৃঙ্খলার জন্য আরও ভয়াবহ হতে পারে।

বার্ষিকী ঘিরে তৎপরতা
ইউক্রেনে রাশিয়ার পুরোমাত্রার অভিযান শুরু হয়েছে তিন বছরের বেশি সময় আগে। তাই হঠাৎ করে এই ইস্যুটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা প্রথমে স্পষ্ট নাও হতে পারে। এর কারণ হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি আবারও যুদ্ধবিরতি বা কোনও ধরনের শান্তিচুক্তির পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন। একবার তিনি বলেছিলেন, মে মাসের প্রথম পূর্ণ সপ্তাহের শেষের আগেই একটি সমাধান হওয়া উচিত।
সম্ভবত এটা কাকতালীয় নয় যে, ওই সময়েই মস্কো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের পরাজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে। ভ্লাদিমির পুতিন সামরিক কুচকাওয়াজে সভাপতিত্ব করবেন।
এতে উপস্থিত থাকবেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।
এমন কুচকাওয়াজ প্রতিবছর হয়। এটি বোঝায় যে, নাৎসি জার্মানির পরাজয় এখনও রাশিয়ার জাতীয় পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু এ বছর ৮০তম বার্ষিকী কিয়েভ ও ওয়াশিংটনের মধ্যে খনিজসম্পদ বিষয়ক চুক্তি ও শি জিনপিংয়ের উপস্থিতি মিলিয়ে এই অনুষ্ঠান বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।
ট্রাম্পের যুদ্ধ বন্ধের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে পুতিন ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে, বার্ষিক অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি সাময়িক যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেবেন। এতে বোঝা যাচ্ছে, পুতিনের উদ্দেশ্য কেবল ইউক্রেনীয়দের রক্ষা করা নয়, বরং একাধিক রাজনৈতিক সমস্যা একসঙ্গে সামলানো।
এই ঘোষণা ট্রাম্পের প্রতি পুতিনের সহানুভূতির প্রকাশও বটে। এতে করে তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে এমন একজন হিসেবে তুলে ধরতে পারেন, যিনি এই “পবিত্র ছুটি” বিঘ্নিত করতে পারেন।
যুদ্ধবিরতির ফলে বিশিষ্ট অতিথিদের ওপর হামলার ঝুঁকিও কিছুটা কমবে। এক ইউক্রেনীয় বিশ্লেষক মনে করেন, পুতিন চান না যে কুচকাওয়াজের দিন তাকে “শি ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের ইউক্রেনীয় ড্রোন থেকে রক্ষায় লেনিনের সমাধিতে লুকিয়ে রাখতে হোক”। যদিও এই ড্রোন ইতোমধ্যে রাশিয়ার গভীরে আঘাত হানার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।
অন্যদিকে জেলেনস্কি বহুবার যুদ্ধবিরতির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু বন্ধ করা। তবে ট্রাম্পের প্রভাবে পুতিন ও জেলেনস্কি কোনও সমঝোতায় পৌঁছালে এর প্রভাব অনেক গভীর হবে।
কারণ যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা সামনে আসায় এখন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আবার আলোচনায় এসেছে— রাশিয়ার দখল করা অঞ্চলগুলোর স্বীকৃতি, বিশেষ করে ক্রিমিয়া; ন্যাটো নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা; এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক শৃঙ্খলার ভবিষ্যৎ।
সংকুচিত ইউক্রেন
দখল করা ইউক্রেনীয় ভূখণ্ড, বিশেষ করে ক্রিমিয়া ও এর গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর সেভাস্তোপলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল একটি কাজ হবে। মনে হচ্ছে, ট্রাম্প প্রশাসন সম্ভাব্য কোনও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তিতে ক্রিমিয়াকে দখল করা অন্য অঞ্চলগুলোর চেয়ে ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে চায়। এজন্য ইতিহাসে ফিরে তাকানো দরকার।
১৯৯১ সালের ১ ডিসেম্বর। একটি গণভোটের মাধ্যমে ইউক্রেন মস্কো থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, সেই নির্বাচন ছিল অবাধ ও সুষ্ঠু। ওই ভোটে দেশের সব অঞ্চলে— এমনকি ক্রিমিয়াতেও স্বাধীনতার পক্ষে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন ছিল।
পুরো ইউক্রেনে ৯০ শতাংশের বেশি ভোটার রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে মত দেয়। বিশ্ব নেতারা, এমনকি সে সময়ের রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনও ইউক্রেনের ১৯৯১ সালের সীমানা, যার মধ্যে ক্রিমিয়াও ছিল, স্বীকৃতি দেন।
এই স্বীকৃতি ও ১৯৯৭ সালের রুশ-ইউক্রেন চুক্তি অনুযায়ী, উভয় দেশ বিদ্যমান সীমান্ত অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। তবুও ২০১৪ সালে পুতিন রুশ বাহিনী দিয়ে ক্রিমিয়া দখল করেন এবং এক তরফা গণভোটের মাধ্যমে অঞ্চলটির রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি ঘোষণা করেন।

১৯৯১ সালের গণভোটের বিপরীতে, ২০১৪ সালের ভোট আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। কারণ এটি একটি কার্যত সামরিক দখলের পরিবেশে অনুষ্ঠিত গণভোট ছিল। খুব কম দেশই এই সংযুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
সম্ভাবনা অনেক বেশি যে, ইউক্রেনকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য ক্রিমিয়া (এবং অন্যান্য দখলীকৃত অঞ্চল) ছাড়া চলতে হবে। বাইডেন প্রশাসনের মেয়াদ শেষের দিকে এসে পরিষ্কার হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা কমে আসছে। সেই সহায়তা থাকলে কিয়েভ দখল করা অঞ্চল ফিরিয়ে আনতে পারত। কিন্তু এখন সেই সম্ভাবনা হ্রাস পাচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলো সহায়তার ঘাটতি পূরণে এখনও সক্ষম নয়, যদিও তারা সে চেষ্টায় আছে।
তবে কোনও সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি এই দখলকে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করবে, তা পরিষ্কার নয়। মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র হয় শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে, নয়তো এর পাশাপাশি অন্তত ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে পারে। এর ফলে ইউক্রেন একটি “সংকুচিত রাষ্ট্রে” পরিণত হবে, যার ১৯৯১ সালের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জোরপূর্বক কেটে নেওয়া হয়েছে।
তবে একটি ভালো বিকল্প হতে পারে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো ও পশ্চিম জার্মানির শীতল যুদ্ধের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সেগুলো দখল করে নেয়।
তবুও যুক্তরাষ্ট্র কখনও সেই দখলকে স্বীকৃতি দেয়নি। একইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি দুই ভাগে বিভক্ত হলেও যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানি পূর্ব জার্মানিকে কখনও স্বীকৃতি দেয়নি। বরং তারা ধারাবাহিকভাবে বলেছে, একটি ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতি এখনও বিদ্যমান, কেবল দুই ভাগে বিভক্ত অবস্থায়।
এই চুক্তিগুলোর মাধ্যমে দুই জার্মানির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম জার্মানি এসব সম্পর্ককে আন্তঃজার্মান সম্পর্ক বলে গণ্য করত, বিদেশি সম্পর্ক নয়।
পূর্ব জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের তারা শুরু থেকেই নিজেদের নাগরিক বলে বিবেচনা করত। এমন কৌশলী অবস্থান ভবিষ্যতের জন্য দরজা খোলা রেখেছিল। ১৯৮০-এর দশকে মিখাইল গর্ভাচেভ ক্ষমতায় এলে সেই ভবিষ্যৎ বাস্তব হয়। ইউক্রেনের জন্যও তেমন একটি আশার পথ উন্মুক্ত রাখা উচিত বলে মনে করেন অনেকে।
সীমান্ত নির্ধারণের গুরুত্ব
যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর ক্রিমিয়া এবং অন্যান্য দখলকৃত অঞ্চলগুলোকে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হবে, তা কেবল ইউক্রেনের জন্য নয়, গোটা ইউরোপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।
ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে সম্প্রতি বলেন, শান্তিচুক্তিতে যদি রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সেটি হবে এক বিষয়। কিন্তু যদি শুধু দখলের বাস্তবতা মেনে নেওয়া হয়, সেটি হবে আরেক বিষয়। যদিও এই দুই অবস্থানের কোনোটাই মাঠপর্যায়ে তেমন পার্থক্য আনবে না। তবে ইউক্রেন থেকে ট্রাম্পের চাপে পুতিন বৈধ স্বীকৃতি আদায় করে নিলে আশপাশের দেশগুলোর জন্য তা হবে ভয়াবহ সংকেত।
এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেন?
কারণ, পুতিনের ইউক্রেন অভিযান ছিল শীতলযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের এক বড় ধাক্কা। তখন পর্যন্ত ধারণা ছিল, ইউরোপে আর কোনও পরাশক্তি বলপ্রয়োগে সীমান্ত পরিবর্তন করবে না। যদিও ছোটখাটো সংঘাত হয়েছিল— যেমন সাবেক যুগোস্লাভিয়া অঞ্চলে— বড় পরিসরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো সংঘাত ইউরোপে নিষিদ্ধ বলেই বিবেচিত ছিল। পুতিন ২০১৪ সালেই সীমান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। তবে তা ছিল তুলনামূলকভাবে কম সহিংসতায়। ২০২২ সালে পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসনই সবাইকে চমকে দেয়।
যুক্তরাষ্ট্র ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার দখলকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলে এটি হবে বলপ্রয়োগে সীমান্ত পরিবর্তনকে বৈধতা দেওয়া। এর ফলে ২০২২ সালের পর দখল করা অন্যান্য অঞ্চল নিয়েও বৈধতা দেওয়ার রাস্তা খুলে যাবে। এর মাধ্যমে ইউরোপের সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে গভীর সন্দেহ তৈরি হবে এবং ইউরোপীয়রা কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বে। তারা হয়তো সীমান্ত অখণ্ডতার নীতি ধরে রাখবে। নয়তো যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের সঙ্গে আপস করতে হবে।
এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, রাশিয়া আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। আগে থেকেই সন্দেহ করা হচ্ছে, তারা বাল্টিক সাগরের নিচে কেবল নষ্ট করছে এবং ইউরোপসহ বিশ্বব্যাপী সাইবার হামলা চালাচ্ছে। এসব কার্যক্রম আরও বাড়বে। এতে উত্তেজনা ও সংঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এমনকি ন্যাটোর জন্য মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে।

পশ্চিমা জোটের পতন
ন্যাটো জোটের মূল ভিত্তি হলো এর প্রতিষ্ঠাতা চুক্তির ধারা ৫। এই ধারায় বলা আছে, কোনও এক সদস্যের ওপর হামলা হলে তা সবার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে সেখানে সরাসরি যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা নেই। বরং একটি কৌশলগত অস্পষ্টতা রাখা হয়েছে।
দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসন যখন ইউরোপকে অবহেলা করে এবং অন্য অঞ্চলে নিজেদের অগ্রাধিকার দেখায়, তখন এই অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে যায়। একবার একটি ‘সিগন্যাল’ চ্যাটে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সসহ ট্রাম্পের শীর্ষ কর্মকর্তারা ইউরোপ নিয়ে তীব্র অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেন। আর তা ‘অপ্রত্যাশিতভাবে’ এক সাংবাদিকের নজরে পড়ে যায়।
কোনও শান্তিচুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র পুতিনের জোরপূর্বক দখলকে বৈধতা দিলে পুতিন তা ব্যবহার করে ন্যাটোর ধারা ৫-এর শক্তি পরখ করতে পারেন। তিনি বাল্টিক অঞ্চলে আক্রমণ বাড়াতে পারেন। আর এসব কর্মকাণ্ডের কোনও জবাব না দেওয়া হলে ‘ধারা ৫’ পুরোপুরি অকার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। এতে ইউরোপ এক প্রকার ‘পোস্ট-ন্যাটো’ যুগে প্রবেশ করবে। তখন প্রশ্ন উঠবে— এরপর কী হবে?
এই প্রশ্ন আজ বিশ্বজুড়ে আলোচিত হচ্ছে। আমেরিকার রাজনৈতিক বিশ্লেষক স্টেসি গডার্ড ফরেন অ্যাফেয়ার্সে লিখেছেন, ট্রাম্প এমন একটি বিশ্ব চান যেখানে শক্তিশালী নেতারা একত্রে বিশ্বকে ‘বিভক্ত’ করে শাসন করবেন। এই ‘বিভাজনের রাজনীতি’-তে তারা একে অপরের অঞ্চলে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ অঞ্চলে শাসন চালিয়ে যাবেন এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের দমন করবেন।
এই মডেল অনুযায়ী, বিশ্ব তিনটি বড় ভাগে বিভক্ত হবে— বেইজিং, মস্কো ও ওয়াশিংটনের অধীনে। এই অবস্থা চূড়ান্ত রূপ পেলে শি জিনপিং তাইওয়ান দখল করতে পারেন, পুতিন সাবেক সোভিয়েত অঞ্চলসমূহ নিজের করে নিতে পারেন, এমনকি ট্রাম্প চাইলে কানাডা, গ্রিনল্যান্ড বা পানামা দখলের চিন্তা করতে পারেন।
এই রকম বিশ্বব্যবস্থা হলে, শীতলযুদ্ধ-পরবর্তী যুগের প্রতিশ্রুতি— যে ছোট দেশগুলো আর পরাশক্তির খেলনায় পিষ্ট হবে না— তা সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ছোট দেশগুলো নিজেরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার পেয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের পথ বেছে নেয়।
তবে বিশ্লেষকেরা তখনই সতর্ক করেছিলেন যে, এই শান্তির স্থায়িত্ব নিশ্চিত নয়। ১৯৯৩ সালে রাশিয়া-বিশেষজ্ঞ স্টিফেন সেস্তানোভিচ বলেছিলেন, “রাশিয়ার গণতন্ত্র ব্যর্থ হলে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ফিরে আসবে। তখন আমরা হতাশ ও অসহায় হয়ে পড়ব।”
আজকের বাস্তবতায় সেই কথাগুলো সত্য হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো—‘বিভাজিত বিশ্ব’ বাস্তবে রূপ নিলে, ছোট দেশগুলো, বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলো কতটুকু স্বাধীনতা রাখতে পারবে?
এই প্রশ্ন কেবল ইউরোপের জন্যই নয়। বরং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শি জিনপিং পুতিনের ইউক্রেন অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন দিচ্ছেন। অবশ্য ২০২২ সালের শেষ দিকে রাশিয়া যখন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভাবছিল, তখন চীন তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবুও শি ও পুতিনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পারস্পরিক স্বার্থ রয়েছে। চীন চায় নির্বিচারে সস্তা জ্বালানি, আর রাশিয়া চায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
রাশিয়ার অভিযানে সমর্থন দিয়ে শি তার দেশের পররাষ্ট্রনীতি— সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও অনাক্রম্যতার নীতি— ভেঙে দিচ্ছেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে নিজেও নিয়ম ভেঙেছেন। ২০২৩ সালে তিনি চীনের সর্বোচ্চ নেতার দুই মেয়াদের নিয়ম বাতিল করে তৃতীয় মেয়াদে থেকে যান এবং নিজেকে আজীবনের জন্য ক্ষমতায় রাখার পথ তৈরি করেন।
তিনি ও পুতিন মিলে পশ্চিমা উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করতে চান এবং নিজেরা সুবিধাজনক একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে চান।
শব্দের শক্তি
এই প্রেক্ষাপটে ইউক্রেনের সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির প্রকৃত গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যদি এমন একটি চুক্তি হয় যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনও দেশ ইউক্রেনের ভূখণ্ড হারানোকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি না দেয়, তাহলে কিয়েভ ভবিষ্যতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। অন্তত, অন্য কোনও উপায়ে নিজেদের হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের আশা রাখা সম্ভব হবে।
আদর্শভাবে এই ধরনের চুক্তিতে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে ন্যাটোর হতে ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলোর সেনা নিয়ন্ত্রণ রেখার পাশে মোতায়েন থাকবে। সেই সঙ্গে ইউক্রেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ পাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা উচিত।

এটি সম্ভব না হলে কোরীয় যুদ্ধের মতো যুদ্ধবিরতি চুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া উত্তম হবে। সেটি এমন কোনও চুক্তির চেয়ে ভালো হবে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখল, এমনকি অন্যান্য অঞ্চল দখলকেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়।
এই চুক্তি এমন এক সময়ে আসতে পারে যখন পুতিন দাবি করবেন যে রাশিয়ার ক্ষমতা একসময় বার্লিন পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এমন একটি চুক্তি ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর বার্তা হতে পারে। এটি মস্কোর জন্য আরও পশ্চিমমুখী শক্তিপ্রসারণের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে এবং বিশ্বকে স্পষ্ট করে দিতে পারে যে, ‘স্ফিয়ার অব ইনফ্লুয়েন্স’ ভিত্তিক ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরু হয়ে গেছে।
এই ধরনের পরিণতির প্রতিধ্বনি তাইওয়ান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। যদিও সেখানে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে—যেমন, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৯ সালে তাইওয়ানকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া বন্ধ করে এবং পরিবর্তে চীনের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। তবুও রাশিয়াকে তার ভূমি দখলের জন্য পুরস্কৃত করা হলে, সেটি একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
এসব কারণে সামনে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে স্বাক্ষরিত হতে পারে এমন একটি চুক্তিপত্রের কয়েকটি শব্দ অনেক বড় অর্থ বহন করতে পারে। বিজয় দিবসে ব্যান্ড বাজবে, পতাকা ওড়ানো হবে—এইসব উদযাপন হবে অতীতকে ঘিরে। কিন্তু এই কাগজে লেখা কিছু শব্দ ভবিষ্যতের জন্য এক অন্ধকার যুগের সূচনা ঘোষণা করতে পারে।
তথ্যসূত্র : এফটি।