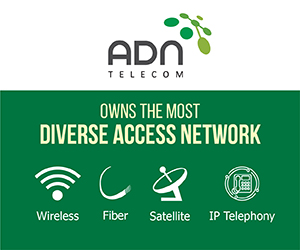যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯০-এর দশকে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে দুটি প্রধান অগ্রাধিকার ছিল। প্রথমত, সদ্যস্বাধীন ইউক্রেন যেন তার বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করে। দ্বিতীয়ত, উত্তর কোরিয়া যেন পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে- তা নিশ্চিত করা।
প্রথম প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তবে আজ অনেকেই মনে করেন, ইউক্রেনের নিরস্ত্রীকরণ ছিল কৌশলগতভাবে একটি বড় ভুল। এই নিরস্ত্রীকরণ ইউক্রেনকে রাশিয়ার অভিযানের মুখে দুর্বল করে ফেলে। এর ফলেই ইউরোপে প্রজন্মের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপে অনীহা কাজে লাগিয়ে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এখন তারা বৈশ্বিক নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা রাখে।
ইসরায়েল এখন দাবি করছে— ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের কাছাকাছি চলে এসেছে এবং তা ঠেকাতে তারা সামরিক অভিযান শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে আগের উদাহরণগুলো বিশ্বজুড়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
প্রশ্ন উঠছে— যে দেশগুলো অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, তাদের কি টিকে থাকার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র থাকা জরুরি? না কি, এই অস্ত্র অর্জনের চেষ্টাই এতটা বিপজ্জনক যে, প্রতিপক্ষরা আগেভাগেই হামলা করে বসে?

আগে মূলত লিবিয়া, সিরিয়া ও ইরাকের মতো রাষ্ট্রগুলো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করত। কিন্তু এখন তা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলো—যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, পোল্যান্ড, জার্মানি ও তুরস্ক।
এই দেশগুলো চিন্তিত যে, তারা হয়তো আর যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষার ওপর নির্ভর করতে পারবে না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কিছু পদক্ষেপ এই শঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তিনি ন্যাটোর গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা বন্ধ করেন এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সরিয়ে নেওয়ার চিন্তাও করেন।
উত্তর কোরিয়া এই সময়ে একঘরে অবস্থা থেকে বেরিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সামরিক জোটে যুক্ত হয়েছে। তারা ইউরোপে সেনা পাঠিয়েছে এবং ইউক্রেনের শহরে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাও চালিয়েছে।
তারা এসব করতে পেরেছে কারণ উত্তর কোরিয়ার সরকার এখন একনায়কতান্ত্রিক এবং তাদের হাতে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে। ফলে তারা সামরিক হুমকিকে ভয় পায় না। ইরানের মতো ধর্মীয় সরকার এমন সাহস দেখাতে পারে না।
ন্যাটোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ট্রাম্প প্রশাসনে ইউক্রেন বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কার্ট ভলকার বলেন, “অনেক দেশ এখন ভাবছে, সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি হলো পারমাণবিক অস্ত্র। আমরা নিজেদের আচরণ পরিবর্তন না করলে ২০ বছর পর এমন এক পৃথিবীতে বাস করব যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের সংখ্যা অনেক বেশি হবে।”
এক নির্মম নতুন বিশ্ব
পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি প্রায় ৮০ বছরের পুরনো। যেকোনো উন্নত শিল্পোন্নত দেশ চাইলেই এটি অর্জন করতে পারে। তবুও পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশের সংখ্যা দীর্ঘদিন খুব সীমিত ছিল।
১৯৬৮ সালের পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) অনুসারে স্বীকৃত পাঁচটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হলো—যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। এরা সবাই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য।
অন্য চারটি পারমাণবিক রাষ্ট্র এনপিটিতে নেই। ভারত ও পাকিস্তান ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে। উত্তর কোরিয়া ২০০৬ সালে তাদের প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালায়।
ইসরায়েল ১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সের সহায়তায় তাদের কর্মসূচি শুরু করে। ধারণা করা হয়, তাদের কাছে কমপক্ষে ৯০টি ওয়ারহেড রয়েছে। তবে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও নিজেদের পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে ঘোষণা করেনি।
যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই তাদের মিত্র দেশগুলোকে নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ছাতার ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দিয়ে এসেছে।
অবশ্য ট্রাম্প প্রশাসনের নানা পদক্ষেপ মিত্রদের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। তবুও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছেন— তাদের নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি এখনও অটুট।
সম্প্রতি ব্রাসেলসে এক সম্মেলনে ন্যাটোতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ম্যাথিউ হুইটাকার বলেন, “আমরা কোথাও যাচ্ছি না। এই বিপজ্জনক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র একা কিছু করতে পারবে না। আমাদের মিত্র দরকার। তবে সেই মিত্রদেরও সক্ষম ও শক্তিশালী হতে হবে, যাতে যুদ্ধ শুরু হলে তারা পাশে দাঁড়াতে পারে।”
তবে এই প্রতিশ্রুতিগুলো অনেকের কাছে এখন কম বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কারণ বিশ্বব্যাপী সংঘাতগুলো ক্রমেই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বড় আকার নিচ্ছে।
চেক প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ান লিপাভস্কি বলেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গত ৮০ বছরে যেভাবে একটি আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছিল, তা এখন ভেঙে পড়েছে। সেই শৃঙ্খলাই পারমাণবিক অস্ত্রসহ বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহারে বিধিনিষেধ তৈরি করেছিল।”
তিনি আরও বলেন, “আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এর জন্য দায়ী ভ্লাদিমির পুতিন। তিনিই এই ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ খুলেছেন। তিনি দেশের সীমানা লঙ্ঘন করছেন। তাই এখন অন্যরাও স্বাভাবিকভাবেই ভাবছে, নিজেদের সীমানা রক্ষা করব কীভাবে?”
১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শার্ল দ্য গল নিজস্ব স্বাধীন পারমাণবিক সক্ষমতা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর না করে এ সিদ্ধান্ত নেন।

আজ এই সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার পরিচয় বলে মনে করে ফ্রান্স। ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু বলেন, “আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, আমাদের নিরাপত্তা অন্য কারও ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না।”
তবে লেকর্নু আরও বলেন, “ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান দেখিয়ে দিয়েছে— পারমাণবিক অস্ত্র একমাত্র সমাধান নয়। পারমাণবিক প্রতিরোধ সব সমস্যা সমাধান করতে পারে না। রাশিয়া একটি পারমাণবিক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও ইউক্রেনে তাদের প্রচলিত সেনাবাহিনী সফলভাবে কাজ করতে পারেনি।
“তিন বছর পরও এক সময়ের শক্তিশালী রুশ বাহিনী ইউক্রেনের চারটি ওবলাস্ট দখল করতে পারেনি। এটি দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের জন্য চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত, বিশেষত উত্তর কোরিয়ার প্রেক্ষাপটে।”
ইউক্রেনের সিদ্ধান্ত ও তার পরিণতি
বিশ্বজুড়ে সরকারগুলো এখন ইউক্রেনের দুর্বলতা ও উত্তর কোরিয়ার নিরাপত্তার মধ্যকার ব্যবধান নিয়ে চিন্তা করছে।
১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পর ইউক্রেন স্বাধীন হয়। তখন রাশিয়া দ্রুত ইউক্রেন থেকে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র সরিয়ে ফেলে। তবে কিয়েভ তখনও প্রায় ১ হাজার ৮০০ কৌশলগত ওয়ারহেড, কৌশলগত বোমারু বিমান ও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের দায়িত্বে ছিল, যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক ভাণ্ডার ছিল।
ইউক্রেন এই অস্ত্রগুলো নিজে থেকে চালাতে পারত না। কিন্তু সে সময়ের কর্মকর্তারা বলেন, ইউক্রেন চাইলেই সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারত। কারণ সোভিয়েত সামরিক শিল্পের একটি বড় অংশ ইউক্রেনে অবস্থিত ছিল।
কিয়েভে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত স্টিভেন পিফার বলেন, “এটি কারও জন্য বিস্ময়কর হওয়া উচিত নয় যে যুক্তরাষ্ট্র এই অস্ত্রগুলো সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। কারণ এগুলো মূলত আমেরিকান শহর ধ্বংসের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।”
অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে ইউক্রেন ১৯৯৪ সালের বুদাপেস্ট স্মারকলিপির অধীনে তাদের পারমাণবিক ভাণ্ডার রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করে। বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়া ইউক্রেনের স্বাধীনতা ও সীমান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ‘নিরাপত্তা নিশ্চয়তা’ দেয়। তবে এই প্রতিশ্রুতিগুলো পরবর্তীতে মূল্যহীন প্রমাণিত হয়।
স্টিভেন পিফার বলেন, “ইউক্রেন সেই সময় পারমাণবিক অস্ত্র রেখে দিলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন কূটনৈতিক পরিণতি হতো। তারা হয়তো উত্তর কোরিয়ার মতো একঘরে হতো না। তবে ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকত না। আর রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতে গেলে পশ্চিমা দিক থেকেও কোনও সহায়তা পেত না।”
২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেন, ইউক্রেনকে পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগে বাধ্য করায় তিনি “ভীষণ অনুতপ্ত” বোধ করেন। তার মতে, ইউক্রেন যদি অস্ত্র না দিত, রাশিয়া হয়তো হামলা করত না।
লিথুয়ানিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোভিলে শাকালিয়েনে বলেন, ২০১৪ সালে রাশিয়া যখন ক্রিমিয়া দখল করে, পশ্চিমা দেশগুলো যথাযথ সহায়তা দেয়নি। এতে বুদাপেস্ট স্মারকলিপি লঙ্ঘিত হয়। তাই ইউক্রেনের উচিত ছিল না অস্ত্র ত্যাগ করা।
তিনি বলেন, “এটি অন্য দেশগুলোকে যে বার্তা দেয় তা হলো— যদি অস্ত্র থাকে, ছাড়বেন না। যদি তৈরি করতে পারেন, তৈরি করুন। সব ধরনের অস্ত্র। কারণ দেখা যাচ্ছে, যেসব দেশের পারমাণবিক অস্ত্র আছে, তাদের খুব একটা আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয় না। ‘চলো নিরস্ত্র হই, শান্তির প্রতীক হই’— এই ধারণা আত্মঘাতী। এখন আমরা সেটা বুঝেছি।”
বর্তমানে ইউক্রেন তার মোট ভূখণ্ডের এক-পঞ্চমাংশ হারিয়েছে রাশিয়ার কাছে। এখন রাশিয়া দাবি করছে, ইউক্রেন যেন বাকি অংশের ওপরও সার্বভৌমত্ব ছেড়ে দেয়। ফলে অনেক ইউক্রেনীয় বিশ্বাস করছেন— ১৯৯০-এর দশকে পারমাণবিক অস্ত্র হস্তান্তর ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত।
তারা উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র যদিও প্রথমে ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়, পরে তা মেনে নেয়। ইউক্রেনও চাইলে ওই পথেই যেতে পারত।
কিছু ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা এমনকি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন— পারমাণবিক অস্ত্রের পথে ফিরে যাওয়ার দরজা এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ইউক্রেনের সাবেক সামরিক প্রধান ও বর্তমানে লন্ডনে রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনি ২০২৫ সালের মার্চে বলেন, “আমাদের এখন পারমাণবিক অস্ত্র নেই, কিন্তু ইউরোপীয় নিরাপত্তার প্রধান প্রতিরক্ষক আমরা।”
তবে ইউক্রেন সরকার জানায়, তারা এখনও পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
উত্তর কোরিয়া গোপনে প্লুটোনিয়াম-ভিত্তিক একটি পারমাণবিক কর্মসূচি গড়ে তোলে। অন্যদিকে, ইরান (এনপিটির সদস্য) ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ-ভিত্তিক একটি বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচি চালায়।

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, এটি আদতে ছিল একটি সামরিক কর্মসূচির ছদ্মবেশ। এই কর্মসূচির জন্য ইরানকে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়েছে— সরাসরি ব্যয় ও নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মিলিয়ে। তবু এই কর্মসূচি ইসরায়েলি হামলা ঠেকাতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে।
কার্নেগি এনডাউমেন্টের জ্যেষ্ঠ গবেষক কারিম সাদজাদপুর বলেন, “এই কর্মসূচি কৌশলগত সম্পদ নয় বরং একটি বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।”
তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, “এই যুদ্ধ শেষ হলে, ইরানের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব হয়তো এটিই মনে করবে যে, ভুল ছিল পারমাণবিক কর্মসূচি চালানো নয়— ভুল ছিল, আরও দ্রুত না চালানো।”
এনপিটি তবে কি শেষ
ইরানের প্রতিবেশীরাও বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তুরস্কে কিছু টিভি বিশ্লেষক ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ ইতোমধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের মতে, ইসরায়েলকে প্রতিহত করতে তুরস্ককেও পারমাণবিক শক্তি হওয়া উচিত।
যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘে ফ্রান্সের সাবেক রাষ্ট্রদূত জেরার্ড অ্যারো বলেন, “মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে ইসরায়েল ও তুরস্কের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কারণ ইরান ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে।”
তিনি আরও বলেন, “একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ যখন আক্রমণাত্মকভাবে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে, তখন আমি যদি তুর্কি কৌশলবিদ হতাম, পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় নিতাম।”
তুরস্ক ও অন্যান্য সম্ভাব্য পারমাণবিক রাষ্ট্রের জন্য এই পথে যাত্রা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল হতে পারে।
বর্তমান পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো চায় না তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব কমে যাক। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ঐতিহাসিকভাবে এনপিটি লঙ্ঘনের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে।
তবে এখন এই আন্তর্জাতিক ঐক্য ভেঙে পড়ছে।
বিশেষ করে রাশিয়া যে এনপিটি মেনে চলবে— এটি এখন প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ তারা উত্তর কোরিয়া ও ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং এমন প্রযুক্তি স্থানান্তর করেছে যার পারমাণবিক প্রয়োগ থাকতে পারে।
১৯৯০-এর দশকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় অংশ নেওয়া এবং ইউক্রেনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাভলো ক্লিমকিন বলেন, “এনপিটি এখনও মৃত নয়, তবে এটি এখন সংকটে রয়েছে।”
তিনি বলেন, “যেসব দেশ মনে করে তারা চুক্তি রক্ষা করেও নিরাপদ নয়, তারা নতুন কিছু চিন্তা করতে শুরু করবে। তখন এনপিটি আর টেকসই থাকবে না।”
পারমাণবিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, কোনো শিল্পোন্নত দেশের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করতে দুই থেকে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে। তবে এই সময়সীমা তখনই বাস্তবায়নযোগ্য, যদি দেশটি আগ্রাসনের শিকার না হয়। যেমন, ইসরায়েল ২০০৭ সালে সিরিয়ার ও ১৯৮১ সালে ইরাকের পারমাণবিক কর্মসূচি সামরিক হামলার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়।
উত্তর কোরিয়াও হয়তো অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে পারে, বিশেষ করে তাদের প্রতিবেশী দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে।
হাওয়াইভিত্তিক এবং পেন্টাগনের অধিভুক্ত থিঙ্ক-ট্যাংক ড্যানিয়েল কে. ইনোয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক সেন্টার ফর সিকিউরিটি স্টাডিজের অধ্যাপক লামি কিম বলেন, “ইরানে যা ঘটছে, তা দেখে দক্ষিণ কোরিয়াবাসী পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আবার ভাবছে। উত্তর কোরিয়ার জন্য এটি ঠেকানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। কারণ দক্ষিণ কোরিয়া প্রচলিত সেনাবাহিনীতে অনেক বেশি শক্তিশালী।”
পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা সস্তা নয়। অস্ত্র তৈরি ও তা বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে কয়েক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে। যদি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, তাহলে ব্যয় আরও বেড়ে যেতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এবং ফ্লোরিডার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ব্রায়ান মাস্ট বলেন, “সবাই চায় যেন তারা নিজ সক্ষমতার চেয়ে বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে পারে, আর পারমাণবিক শক্তি এ সুযোগ দেয়।”
তবে অতীতে অনেক দেশই পারমাণবিক অস্ত্রের পথে হাঁটার চিন্তা করেও পিছিয়ে গেছে। তারা বলেছে, “আমরা সত্যিই এটি করতে পারি না। কারণ এটি করতে গেলে অন্য সব কিছু বাদ দিতে হবে, যদিও আমাদের আগ্রহ ছিল।”
যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পারমাণবিক শক্তিধর দেশ দীর্ঘদিন ধরে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের পক্ষে যুক্তি দিয়ে আসছে। তাদের মতে, যদি বিশ্বে বহু দেশ পারমাণবিক অস্ত্রধারী হয়ে যায়, তবে বৈশ্বিক নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে পড়বে।
তারা মনে করে, এর ফলে মানবজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। ২০১৯ সালের মে মাসে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

ব্রায়ান মাস্ট বলেন, “তখন বিশ্বজুড়ে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ সরাসরি মুখোমুখি অবস্থানে ছিল।”
তবে অনেকের মতে, ওই সংঘাত দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি। কারণ উভয় পক্ষই পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখাতে পেরেছিল।
এই বিষয়টি দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হতে পারে। কারণ তারা মনে করছে, উত্তর কোরিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে তাদের কৌশলগত অবস্থান এখন আরও ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।
উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা এবং পারমাণবিক অস্ত্রের শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। এখন তারা যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডকেও হুমকির মুখে ফেলতে সক্ষম। এর ফলে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে রক্ষা করার জন্য সামরিক পদক্ষেপ নিতে দ্বিধায় পড়তে পারে।
এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ কোরিয়াও সেই একই সমস্যার মুখে পড়েছে, যে সমস্যার কারণে ফ্রান্স পারমাণবিক অস্ত্রের পথে গিয়েছিল।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট দ্য গল একবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডিকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আপনারা কি নিউ ইয়র্ক শহর ধ্বংসের ঝুঁকি নিয়ে প্যারিস রক্ষার জন্য প্রস্তুত?” কিন্তু তিনি পরিষ্কার কোনও উত্তর পাননি।
বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় জনমত বলছে— বেশিরভাগ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতিকে যথেষ্ট মনে করে না। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন, দেশটির নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিত।
বার্লিনে জার্মান ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স-এর কোরিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এরিক বালবাখ বলেন, “এখন পারমাণবিক অস্ত্রের পক্ষে জনমত মূলধারার মধ্যেই রয়েছে।”
তিনি বলেন, এই সমর্থন শুধু রক্ষণশীলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লি জে-মিউংয়ের নেতৃত্বে মধ্য-বাম রাজনৈতিক শ্রেণিতেও ছড়িয়ে পড়েছে।
পুসান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক রবার্ট ই. কেলি বলেন, “ট্রাম্প যে মিত্রদের জন্য পারমাণবিক ঝুঁকি নেবেন না, তা একদম স্পষ্ট। আমি বহু গবেষণাপত্রে যুক্তি দিয়েছি, সিউলের উচিত নিজেদের স্বতন্ত্র পারমাণবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।”
রবার্ট কেলি বলেন, “কেউই বিশ্বাস করে না যে দক্ষিণ কোরিয়া হঠাৎ করে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করবে। কেউ ভাবছে না যে, পোল্যান্ড যদি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে, তাহলে তারা তা মস্কোর ওপর ফেলে দেবে।
“এরা গণতান্ত্রিক দেশ। যদি তারা পারমাণবিক অস্ত্র বানায়, তাতে সমস্যা নেই। কেবল আমেরিকার আত্মম্ভরিতা থেকেই আমরা ধরে নিই, শুধু তারাই এসব অস্ত্র ব্যবস্থাপনা করার জন্য যথেষ্ট দায়িত্বশীল।”
তথ্যসূত্র : ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল