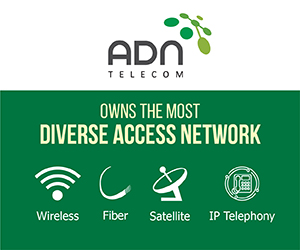সিংহ দরবারের সিংহদ্বারগুলোর খটখট শব্দ ড্রামের চেয়ে জোরে বাজছিল, শেষে টিকতে পারল না, সমুদ্রের মতো জনস্রোতে চৌচির হয়ে গেল। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও ক্ষমতা আগলে রাখতে পাহারাদারের মতো তা দাঁড়িয়েছিল।
রাষ্ট্রনেতাদের এই অফিস শুনছিল জনতার পায়ের আওয়াজ। উত্তেজিত সেই জনতা ভাঙছিল জানালা, নানা নিদর্শন; নিয়ে যাচ্ছিল বিলাসবহুল চাদর কিংবা জুতা, যে যা পাচ্ছিল।
এই ভবন ছিল ক্ষমতার প্রতীক। দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে তা ছিল দুর্ভেদ্য, ধরাছোঁয়ার বাইরে। অল্প সময়ের জন্য হলেও তা আক্ষরিক অর্থেই জনগণের মালিকানায় চলে এসেছিল।
এমন চিত্র দেখা গেল গত সপ্তাহে নেপালে। ২০২২ সালে তা দেখা গিয়েছিল শ্রীলঙ্কায়, তার দুই বছর বাদে ২০২৪ সালে দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশে। তিনটিই দক্ষিণ এশিয়ার দেশ।
৩ কোটি মানুষের দেশ নেপাল যখন ঐতিহ্যবাহী নির্বাচনী গণতন্ত্রের বিপরীতে অচেনা এক উপায়ে তার ভবিষ্যৎ সাজাচ্ছে, তখন তরুণদের নেতৃত্বে একের পর এক সরকার উৎখাত একটি বড় প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসছে; দক্ষিণ এশিয়া কি জেন জি বিপ্লবের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে?
যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক পল স্ট্যানিল্যান্ড, যার গবেষণার কেন্দ্র দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক সহিংসতা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, তিনি বলছেন, “এটি অবশ্যই অভূতপূর্ব। এক ধরনের নতুন অস্থিতিশীল রাজনীতি দেখা যাচ্ছে।”
সোশাল মিডিয়া বন্ধের পর জেন জিদের তিন দিনের সহিংস বিক্ষোভে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। এরপর প্রায় ১০ হাজার তরুণ অনলাইনে একটি ভোটের মাধ্যমে একজন অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বেছে নিয়েছে।
অথচ শুরুতে এই বিক্ষোভকে ‘জেন জি বিক্ষোভ’ নামে উপহাসই করা হচ্ছিল। তবে তারা দেখিয়ে দিয়েছে সরকার হটিয়ে, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলোর তরুণরা বোঝাতে চাইছে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। তাই নিজেরাই ক্ষমতা দখল করছে।
স্ট্যানিল্যান্ডের চোখে এটি নাটকীয় পরিবর্তন। কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান বা রাজনৈতিক সংঘাতের আগের রূপের চেয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।
শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালের প্রতিটি বিক্ষোভের সূচনা আলাদা কারণে হলেও বিশ্লেষকরা তার মধ্যে একটি সাধারণ সূত্র খুঁজে ফিরছেন।
তারা বলছেন, এই প্রজন্ম ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঁচতে অস্বীকার করছে এবং সেই কারণই তাদের চালিত করেছে এই পথে। তারা একে অন্যের কাছ থেকেও শিখছে।
কলম্বো থেকে ঢাকা হয়ে কাঠমান্ডু
কাঠমান্ডুতে জেন-জি বিক্ষোভ শুরু হয় যখন সরকার নেপালের নিয়ম না মানার কারণ দেখিয়ে অধিকাংশ সোশাল মিডিয়া অ্যাপ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু বিক্ষোভের কেন্দ্র ছিল আরও গভীরে: বৈষম্য, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি।
হাজার হাজার তরুণ রাস্তায় নেমে আসে, যাদের একটি বড় অংশ স্কুৃল পোশাকেই নামে বিক্ষোভে। তা দমনে কঠোর হয় সরকার। তাতে ৭০ জনেরও বেশি নিহত হয়, আহত হয় শত শত।
কিন্তু এই দমননীতি পরিস্থিতি শান্ত করার বদলে সঙ্কট আরও বাড়িয়ে তোলে। বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্ট ভবনে আগুন দেয়, আগুন দেয় প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সিংহ দরবারে, আক্রমণ করে রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে। প্রধানমন্ত্রী ওলির বাড়িতে ঢুকেও লুটপাট চলে। শেষে ওলি পদত্যাগ করেন।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল ভিন্ন কারণে। সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে সেই আন্দোলনে নেমেছিল শিক্ষার্থীরা। তারা বলছিল, কোটা বৈষম্যমূলক। বাংলাদেশেও বিক্ষোভ দমনে কঠোর হয়েছিল সরকার। তাতে শত শত মানুষের মৃত্যুতে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়, যার পরিণতিতে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। এরপর তার সরকারি বাড়ি, কার্যালয়, পার্লামেন্ট ভবনে চলে গিয়েছিল জনতার দখলে।
তার দুই বছর আগে শ্রীলঙ্কার বিক্ষোভের কেন্দ্রে ছিল অর্থনৈতিক সঙ্কট। শ্রীলঙ্কা সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়ায় ২০২২ সালের মার্চের মধ্যে মানুষের জীবন-যাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বিদ্যুৎ নেই, জ্বালানি তেল নেই, মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে নেমেছিল রাস্তায়।
তরুণরা কলম্বোয় প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের সামনে একটি প্রতিবাদ শিবির স্থাপন করেছিল, যার নাম দেয় ‘গোটাগোগামা’। তা ছিল দেশটির প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের প্রতি ইঙ্গিত করে, যার পরিবার গত ১৮ বছরের মধ্যে ১৫ বছর দেশটি শাসন করেছিল।
জুলাইয়ের মাঝামাঝিতে বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্টের বাড়িতে ঢুকে পড়ে; গোতাবায়া রাজাপাকসেকে সপরিবারে দেশ ছাড়তে হয়।
মিল-অমিল
হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক উপ-পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলীর মতে, এই তিনটি দেশে তরুণদের আন্দোলনে শক্তিশালী সরকারগুলোর উৎখাতের পেছনে একটি সাধারণ ভিত্তি রয়েছে। তা হচ্ছে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং অভিজাত রাজনীতিকদের দুর্নীতি।
জেন জি তাদের জীবনে দুটি অর্থনৈতিক মন্দা দেখেছে। ২০০৮-০৯ সালে এবং তারপর কোভিড মহামারিকালে।
মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, এই প্রজন্ম তাদের মনোগঠনের দুটি বছর আইসোলেশনে কাটিয়েছে, শারীরিকভাবে তারা বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু এই সময়কালে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তারা উপস্থিতি বাড়িয়ে দেয়।
এই সবকিছু এমন সময়ে ঘটছিল যখন তাদের শাসন করছিল দাদা-দাদির বয়সের নেতারা। যেমন নেপালের ওলির বয়স ৭৩ বছর, বাংলাদেশের শেখ হাসিনার ৭৬ বছর এবং শ্রীলঙ্কার রাজাপাকসের ৭৪ বছর।

গাঙ্গুলী বলেন, “দক্ষিণ এশিয়ার তরুণরা তাদের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে নিজেদের সংযোগ স্থাপনের মতো কিছু খুঁজে পায়নি।”
বিক্ষোভের শুরুর অমিল থাকলেও জেন জিরা তাদের জীবন এবং রাজনীতিক ও তাদের সন্তানদের জীবনের মধ্যে ফারাকটি দেখেই ক্ষুব্ধ ছিল।
স্ট্যানিল্যান্ড বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় আন্দোলনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মিল যেখানে, তা হচ্ছে একটি ভালো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের কল্পনা করার ক্ষমতা।
তার মতে, বঞ্চনার অনুভূতি এই তরুণদের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত চাওয়ার প্রশ্নে এক করেছে।
এই তিনটি দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকর বয়স ২৮ বছরের নিচে। দেশগুলোর জিপিডি বিশ্বের গড় জিডিপির চেয়ে কম। কিন্তু সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের বেশি।
বিশেষজ্ঞরা বলছে, তরুণদের এই আন্দোলনগুলো আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচ্ছিন্ন কোনও বিষয় নয়। সেই কারণে দেশগুলোর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে তা আবেদনময় হয়ে উঠেছে।
জেন জি বন্ধন
ইন্দোনেশিয়ায়ও ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে, সেখানে #NepoKid সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রেন্ডে রূপ নিয়েছিল, যা দেখা গিয়েছিল নেপালেও।
যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স প্রোগ্রামের ফ্যাকাল্টি ডিরেক্টর রুমেলা সেন বলেন, যদি কেউ এই দেশগুলোর বিক্ষোভের সহিংসতার দিকটি আলাদা করতে পারেন, তাহলে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল করে তোলার একটি আকাক্ষার প্রকাশ দেখতে পাবেন।
দেশগুলোতে তরুণদের সংখ্যাধিক্য এবং ইন্টারনেটে তাদের সদর্প উপস্থিতি এই বিক্ষোভ সংগঠন সহজ করে দিয়েছে বলে মনে করেন তিনি। যে কারণে ইন্টারনেট কিংবা সোশাল মিডিয়া অ্যাপ বন্ধ করা সরকারগুলোর জন্য বুমেরাং হয়েছে।

এই বিক্ষোভগুলো ওপর চোখ রেখে নৃতত্ত্ববিদ জীবন শর্মা এক দেশের জেন জিদের অন্য দেশ থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয়টিও দেখতে পাচ্ছেন।
তিনি বলেন, “নেপালি তরুণরা শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের আন্দোলনগুলো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ করছে।”
গবেষণার জন্য এখন কাঠমান্ডুতে রয়েছেন জীবন শর্মা, সেই কারণে সাম্প্রতিক আন্দোলনটি নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তিনি।
তিনি বলেন, এই যে আন্দোলনগুলো, সেগুলো একটি অন্যটির কাছ থেকে শিখছে। অন্যান্য বৈশ্বিক বিক্ষোভ থেকেও শিখেছে, যেমন ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সের।
স্ট্যানিল্যান্ডও একমত হয়ে বলেন, “অবশ্যই, এই আন্দোলনগুলো একে অপরকে দেখছে, শিখছে এবং একে অপরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে।”
এখন প্রশ্ন হলো- শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপালর পথ কোথায়?
তথ্যসূত্র : আল জাজিরা