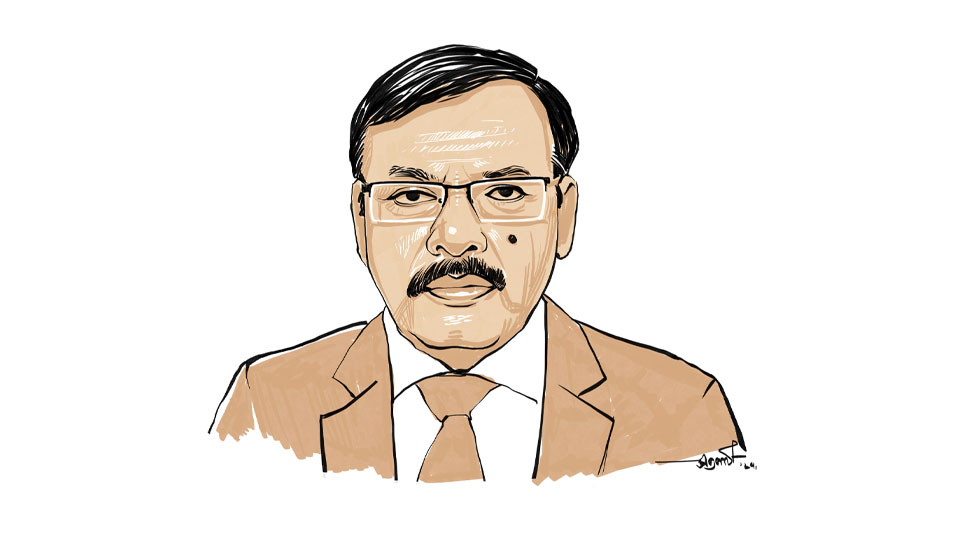নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত সে বইটি এখনও ঢাকার বৃক্ষচর্চার আকরগ্রন্থ। তিনি শ্যামলী নিসর্গ লিখে রেখে না গেলে সেকালের ঢাকার পথতরুর বৃত্তান্ত আমরা হয়ত জানতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকার সেসব পথতরুর এখন কী অবস্থা? আজও কি সেগুলো বেঁচে আছে? দ্বিজেন শর্মার আত্মজ সে বৃক্ষরা এখন ঢাকার কোথায় কীভাবে আছে সে কৌতুহল মেটানো আর একালের পাঠকদের সঙ্গে ঢাকার সেসব গাছপালা ও প্রকৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে এই লেখা। কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সরেজমিন অনুসন্ধানে তুলে ধরছেন ঢাকার শ্যামলী নিসর্গের সেকাল একাল। ঢাকার প্রাচীন, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য পথতরুর বৃত্তান্ত নিয়ে সকাল সন্ধ্যার পাঠকদের জন্য বাংলা বারো মাসে বারো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পড়ুন অগ্রহায়ণ পর্ব।
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: কার্তিক পর্ব
বাংলায় কোম্পানি শাসন শুরু হয় ১৭৫৭ সালে। ১৮২৫ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ডয়েস মোগল আমলের ঢাকা শহরটিকে পাকা রাস্তা, খোলা জায়গা, রাস্তার আলো, পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ইত্যাদিসমৃদ্ধ একটি আধুনিক শহরে পরিণত করেন। ডয়েস নওয়াবপুরের উত্তর-পূর্ব অংশ পরিষ্কার করে এলাকাটিতে সেনা ছাউনি স্থাপন করেন। এ এলাকাটিই পরে পুরান পল্টন নামে পরিচিত হয়। ১৮৫৯ সালে প্রস্তুতকৃত একটি মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, এ সময় ঢাকা নগর দৈর্ঘ্যে সোয়া তিন মাইলের সামান্য বেশি এবং প্রস্থে সোয়া এক মাইলের মতো জায়গা দখল করে আছে। ‘জেমস টেইলরের টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অব ঢাকা’ বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সালে। সে বইয়ে তিনি কোম্পানি আমলে ঢাকার যেসব উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে কর্পূর, কামরাঙ্গা, খিরনি, তেঁতুল, গাব, হিজল, আমলকি, হরিকতী, বহেড়া, কদম, নাগকেশর, চালতা, বেল, আমড়া (বুনো আমড়া), নিম, লটকা, রক্তকাঞ্চন, রক্তচন্দন (রঞ্জনা), বকুল, শিউলি, সজিনা, ডেউয়া, পলাশ, সোনাইল, ঝাউ ইত্যাদি বৃক্ষের নাম রয়েছে। অর্থাৎ কোম্পানি আমলেও ঢাকায় এসব গাছ ছিল। কিন্তু সেগুলো ঢাকা শহরেই ছিল না কি বৃহত্তর ঢাকায় ছিল তা নিশ্চিত নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে এর সবগুলো বৃক্ষই এখন ঢাকা শহরে রয়েছে। এই পর্বে সেসব কয়েকটি বৃক্ষের পরিচয় দেওয়া হলো।

কর্পূর গাছ
কর্পূর আমরা সবাই চিনি, বাজারে এটা কিনতে পাওয়া যায়। সাদা রঙের দানাদার সেই বস্তু বাতাসে খোলা রাখলে উবে যায়, পোড়ালে জ্বলে। দুই ধরনের কর্পূর রয়েছে—কৃত্রিম বা রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক। রাসায়নিক দ্রব্য থেকে সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম কর্পূর কারখানায় তৈরি করা হয়, যা সাধারণত বাজারে বিক্রি হয় এবং পূজার সময় তা পোড়ানো হয়, পোড়ানোর পর তা থেকে বিশেষ সুগন্ধ বের হয়। কর্পূর পানিতে গলে না বা মেশে না, কিন্তু ক্লোরোফর্ম, ইথার ও অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। কর্পূর একটি তারপিন (জৈব যৌগ) যা বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী যেমন ক্রিম, মলম, লোশন ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
কর্পূর কাঠ থেকে বাষ্প-পাতন প্রক্রিয়ায় আহরণ করা হয় কর্পূর তেল। কর্পূর তেল ব্যাথা, জ্বলাপোড়া, চুলকানি ইত্যাদি উপশমের জন্য বাহ্যিকভাবে মালিশ করা হয়। কর্পূর তীব্র ঘ্রাণযুক্ত ও ত্বকে সহজে দ্রুত শোষিত হয়। কর্পূরকে স্পর্শ করলে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। রাসায়নিক কর্পূর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়, ওষুধ হিসেবে করা হয় না। ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় প্রাকৃতিক কর্পূর। আজকাল বাজারে যে কর্পূর পাওয়া যায় সেগুলো কর্পূর গাছ থেকে প্রস্তুত নয়, কৃত্রিমভাবে কারখানায় তৈরি। তাছাড়া প্রাকৃতিক কর্পূর তৈরির ক্ষেত্রেও কোনও কোনও দেশে কর্পূর গাছ ছাড়া অন্য গাছ থেকেও তা তৈরি করা হচ্ছে। যেমন শ্রীলংকায় এক ধরনের জংলি কর্পূর গাছ থেকে কর্পূর আহরণ করা হয়, জাপান ও চীনে কর্পূরতুলসি গাছ থেকেও কর্পূর আহরণ করা হয়। কর্পূরতুলসি গাছের সমগ্র অংশকে চুইয়ে বের করা হয় কর্পূর তেল, এরপর তা অন্য আর একটি প্রক্রিয়ায় দানাতে পরিণত করা হয়।

কর্পূর ও কর্পূর তেল তৈরি হয় যে গাছ থেকে সেটাই হলো কর্পূর গাছ। লোকজ চিকিৎসায় শত শত বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে কর্পূর গাছের প্রাকৃতিক উপাদান ঘরে ও ওষুধ গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঘরে কর্পূরের শিখা জ্বালান। এ শিখাকে তারা সবচেয়ে পবিত্র শিখা বলে মনে করেন। কর্পূর ঘরে এক আধ্যাত্মিক শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে। তবে শুধু মানসিক প্রশান্তির জন্য নয়, দৈহিক কিছু সমস্যা কর্পূর দূর করতে পারে।
কর্পূর গাছের আদিনিবাস ভারত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও ভূটান। সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বের আরও অনেক দেশে এ গাছের বিস্তার ঘটেছে। বর্তমানে কর্পূরের জন্য তাইওয়ান, চীন, জাপান, কোরিয়ায় এ গাছ চাষ করা হচ্ছে। এ গাছ দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলংকা, মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে। কর্পূর লরেসী (Lauraceae) গোত্রের Cinnamomum গণের একটি উদ্ভিদ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এ গণের ২০০ থেকে ৩৫০ প্রজাতির গাছ দেখা যায়। এর মধ্যে ভারতেই আছে প্রায় ৪০ প্রজাতির গাছ, বাংলাদেশে আছে ১১টি প্রজাতির গাছ। কর্পূর, তেজপাতা, দারচিনি একই গোত্রের গাছ। পৃথিবীতে মাত্র দুটি প্রজাতির গাছ থেকে কর্পূর আহরণ করা হয় যা বিভিন্ন রোগের ভেষজ ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। প্রজাতি দুটি হলো Cinnamomum camphora ও Cinnamomum agasthyamalayanum। প্রথমোক্ত প্রজাতির গাছ এদেশে আছে, তবে খুব কম দেখা যায়। নাটোর দিঘাতিয়া রাজবাড়ির বাগানে একটি বয়স্ক বড় কর্পূরের গাছ আছে। দ্বিতীয় প্রজাতির গাছ শ্রীলংকার অরণ্যে দেখা যায়।
কর্পূর একটি বহুবর্ষজীবী চিরসবুজ বৃক্ষ, গাছ ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বাকল হলদে-বাদামি, খসখসে। পাতা উজ্জ্বল সবুজ, অবডিম্বাকার, অগ্রভাগ সূঁচাল, ৫-১০ সেন্টিমিটার লম্বা, চকচকে, শিরার রঙ হালকা। পাতা দেখতে খানিকটা ছোট লিচু পাতার মতো, তবে লিচু পাতার চেয়ে পাতলা। পাতা ডললে বা ছেঁচলে তা থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্পূরের ঘ্রাণ বের হয়। কর্পূর গাছের বিভিন্ন অংশের তেলপূর্ণ কোষের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ‘কর্পূর’ বা ক্যাম্ফর তৈরি হয়। ক্যাম্ফর হলো এক ধরনের টারপিনয়েড যৌগ, কর্পূর গাছের বিভিন্ন অংশে যে গন্ধসার তেল থাকে যা সুগন্ধ উৎপাদন করে।
কর্পূর গাছে প্রচুর ডালপালা নিয়ে পাতাগুলো ঘন ছাতা তৈরি করে। এজন্য কেউ কেউ উদ্যানে কর্পূর গাছ লাগান শোভা বাড়ানোর জন্য। ফুল উভলিঙ্গী, রং হলদে সাদা। ফল গোলাকার, থোকায় অনেক ধরে, ফলের রং গাঢ় সবুজ। ফল পাখিরা খায়। বীজ ক্ষুদ্র। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে ও সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে ফল ও বীজ পাকে। ফল দেখতে অনেকটা খুদিজামের মতো, তবে খোসা তার চেয়ে পাতলা। বসন্তকাল বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। আধা-পক্ব ডাল কেটে শাখা কলম বা কাটিং করেও কর্পূরের চারা তৈরি করা যায়। গ্রীষ্মকাল কাটিং করার জন্য ভালো সময়।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বেশ কয়েক প্রকার কর্পূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধন্বন্তরী নিঘুন্টিতে রয়েছে ২ প্রকারের কর্পূর— পক্ব ও অপক্ব কর্পূর। পক্ব কর্পূর হলো যা কর্পূর গাছের কাঠ থেকে সরাসরি পাওয়া যায়। এই কর্পূর পানিতে ভাসে, তীব্র ঘ্রাণযুক্ত ও ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সহজে বাষ্পীভূত হয়। অপক্ব কর্পূর হলো কর্পূর গাছের শাখা প্রশাখা, মূল থেকে যে কর্পূর পাওয়া যায়। এসব অংশ টুকরো টুকরো করে কেটে তাপ দিলে তা থেকে গদ বা রেজিন বের হয়। সর্বাধিক কর্পূর পাওয়া যায় মূল থেকে। উর্ধপাতন পদ্ধতিতে আহরিত সেই রজনকে বলা হয় নির্যাস। অপক্ব কর্পূর পানিতে ডুবে যায়। মৃদু ঘ্রাণযুক্ত ও ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয় না। পক্ব কর্পুরের তুলনায় গুণগত মানে অপক্ব কর্পূর উত্তম।
কর্পূর ব্যাকটেরিয়ানাশক, ছত্রাকনাশক ও ব্যাথানাশক। তাই ত্বকের ও শ্বাসের সমস্যায় কর্পূর ব্যবহার করা যেতে পারে। গবেষণায় মানুষের ভাইরাসজনিত হার্পস রোগের ভাইরাস জীবাণুর বিরুদ্ধে কর্পূর কার্যকর বলে জানা গেছে। মশা বিভিন্ন রোগ জীবাণুর বাহক, যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ইবেলা, জিকা, চিকুনগুনিয়া ইত্যাদি। পতঙ্গ বিতাড়ক হিসেবেও কর্পূর কাজ করে। গুদামজাত শস্যের পোকা নিয়ন্ত্রণে বা বিতাড়নে কর্পূর ব্যবহৃত হয়। কর্পূর ব্যাথার উপশম করতে পারে।
কামরাঙ্গা
কামরাঙ্গার সাথে রাঙ্গা বউয়ের কামনার কি কোনও সম্পর্ক আছে? নাকি কামরাঙ্গার পাকা ফলগুলোকে লাজে রাঙা নতুন বউয়ের মুখের মতো মনে হয়? সে কথা ভাবতেই মনে আসে নজরুলের গানের দুটি পংক্তি:
‘‘ও তুই কারে দেখে ঘোমটা দিলি নতুন বউ বল্ গো,
তুই উঠলি রেঙে যেন পাকা কামরাঙ্গার ফল গো ॥’’
কামরাঙ্গা ফলের গাছ হলেও সে বেশ শোভাময়ী। বিশেষ করে সারা বছরই তার ঘন সবুজ ও তামাটে কচি পাতার মিশেল, ছাতার মতো বিস্তৃত ডালপালা, নিবিড় ছায়া এবং বৈশাখ থেকে শ্রাবণে ফোটা থোকা থোকা লালচে, বেগুনি, গোলাপি রঙের ফুলের প্রাচুর্য সে গাছকে করে তোলে সালংকরা। ফুলগুলোই যেন তখন ডালের ওপর মেয়েদের বাহুর অলংকারের মতো শোভা পায়। কামরাঙ্গা গাছের এই রক্তিম রূপ বহু নিসর্গপ্রেমিকের কাছেই লোভনীয়। তবে ডালে ডালে ঝুলতে থাকা ফলের প্রাচুর্যও কম আনন্দদায়ক না। ফলের গাছ হিসেবে কামরাঙ্গা বাড়ির আঙ্গিনায় সাধারণত লাগানো হয়। উদ্যানে লাগানো হয় উদ্ভিদ বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য। ঢাকা শহরে পথতরু হিসেবে কোথাও কামরাঙ্গা গাছকে নির্বাচন ও রোপণ করা হয়নি। তবে দু’এক জায়গায় লাগালে তার ফল খেতে কাঠবিড়ালী ও পথশিশুরা নিশ্চয়ই সে গাছের কাছে যেত, পথিকদেরও সে ছায়া দিত।

কামরাঙ্গা গাছ বড় আকারের বহু শাখায়িত ঝোপালো প্রকৃতির চিরসবুজ বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ। গাছ ১২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা যৌগিক, একটি ডাটার দু’পাশে ৫-৭ জোড়া পত্রফলক বিপরীতভাবে সাজানো থাকে, শীর্ষ পত্রিকা সজোড়, কচি পাতা তামাটে লাল। গাছের শক্ত কাণ্ড ও ডাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থোকা ধরে ফুল আসে ও ফল ধরে। ফুলের রঙ হালকা গোলাপি। বৈশাখ থেকে শ্রবণে ফুল ফোটে, ফল পাকে ভাদ্র থেকে পৌষ মাসে। ফল মাকু বা ডিম্বাকৃতি, মাংসল, পাঁচটি শির বা খাঁজবিশিষ্ট। কচি ফলের রং সবুজ, পাকলে হয় হলদে সবুজ। পাকা ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি, ফল হিসেবে সাধারণত টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয়। তবে পাকা কামরাঙ্গা ফল থেকে জ্যাম, জেলি, মোরব্বা, আচার ও সুস্বাদু শরবত তৈরি করা যায়। শরবতের সুমিষ্ট গন্ধ ও সুস্বাদ মুখে রুচি আনে। ফল আড়াআড়িভাবে কাটলে হুবহু তাঁরার মতো দেখায়। এজন্য এ ফলের ইংরাজী নাম স্টার আপেল। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম অ্যাভেরোয়া ক্যারামবোলা (Averrhoa carambola) ও গোত্র অক্সালিডেসী (Oxalidaceae)। অ্যাভেরোয়া আরবীয় চিকিৎসাবিদ অ্যাভের্যসের নামের স্মারণিক, ক্যারামবোলা কামরাঙ্গার স্পেনীয় নাম। আদিনিবাস দক্ষিণপূর্ব এশিয়া।
নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে ১৯৬৫ সালে ঢাকা শহরের তাঁর দেখা কামরাঙ্গা গাছের কথা সম্পর্কে লিখেছেন: ‘‘ঢাকায় কোনো পথেই ছায়াতরু হিসেবে এটি রোপিত হয় নি। কোনো ব্যক্তিগত বাগান কিংবা জলা-জঙ্গলপূর্ণ কোনো পতিত জায়গা ছাড়া কোথাও এদের দেখা মেলে না। হাইকোর্টের পূবদিকে পার্ক-এভিনিউর কোল ঘেঁষে যে এক ফালি জঙ্গল সারা শহরের জনকোলাহলে একান্ত বেমানানভাবে অক্ষত, ওখানে একটি কামরাঙ্গা গাছ উপেক্ষা সত্বেও আজও দিব্যি বেঁচে আছে।’’ সেটির সন্ধানে হেমন্তের এক সকালে সেখানে যাই। অবশ্য ঢাকা শহরে এখন কামরাঙ্গা গাছ অনেক স্থানেই আছে। রমনা উদ্যান, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও বলধা গার্ডেনে পুকুর পাড়ে রয়েছে একটি কামরাঙ্গা গাছ।

শোনা
বাংলায় শোনা গাছ অনেক নামে পরিচিত— খোনা, খনা, হোনা, নসোনা, পাত্তি, ডিঙ্গা, কানাইডিঙ্গা, কনক, ভিঙ্গা, থোনা ইত্যাদি। এ দেশের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর কাছে এ গাছ আবার বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন— খনাগুলা (চাকমা), ক্রোংসামি (মারমা), থাকুরুং বাথাই (ত্রিপুরা), খামা (মগ), বাইল্যা (চাকমা), লঙকচ শিম (মুরুং), থাকুরঙ (টিপরা), কেরিঙ বা খেরিং (গারো) ইত্যাদি। হিন্দিতে এ গাছকে বলে ভূতবৃক্ষ। অন্যান্য ভাষায় ভাতঘীলা (অসমীয়া), ভুতক (হিন্দি), শোন (হিন্দি), তেতিলা (সিংহলিজ), কোরি-কোন্নাই বা পুত পুষ্পম (তামিল), মান্দুকা-পরনামু (তেলেগু) ইত্যাদি।
বাকল তোলার পর কাঠের রঙ দেখতে সোনার মতো বলেই হয়ত এ গাছের নাম শোনা, সংস্কৃতে ‘শ্যোণাক’। এর ইংরেজি নাম Broken bones plant, Indian calosanthes, Indian Trumpet, tree of Damocles ইত্যাদি।
শোনা এ উপমহাদেশের গাছ। ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে, ভূটানে, চীনের দক্ষিণাংশে এ গাছ জন্মে থাকে। ভারতের অন্ধ্রপদেশ, রাজস্থান ও আসামেও এ গাছ আছে। থাইল্যান্ড, নেপাল ও শ্রীলংকায় এ গাছ জন্মে থাকে। এ দেশে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, দিনাজপুর ও ঢাকা-টাঙ্গাইলের জঙ্গলে শোনা গাছ দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের শালবনেও এ গাছ আছে এমনকি সুন্দরবন সংলগ্ন জনপদের জঙ্গলেও এ গাছ জন্মে। বসতবাড়ির বাগানেও এ গাছ জন্মে থাকে।

শোনা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর গাছ। পাহাড়ের ঢালে ভালো জন্মে। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। বেলে দোঁয়াশ মাটিতে এ গাছ ভালো জন্মে। এ গাছের শিকড়ের মাটিতে এক ধরনের একটিনোমাইসিটি অণুজীবের উপস্থিতিতে তার সাথে সংঘবদ্ধতা বা সম্পর্ক করে শোনা গাছ বেঁচে থাকে। এই গাছ পরিবেশগত প্রতিকূলতা সহ্য করতে পারে। তবে অত্যধিক গরম ও ঠাণ্ডা এ গাছের জন্য ক্ষতিকর।
শোনা একটি বহুবর্ষী চিরসবুজ স্বভাবের বৃক্ষ। কাণ্ড শাখায়িত। তবে গাছ খুব ঝোপালো হয় না। বাকল খুব মোটা। ভেতরটা পাকা সোনার মতো রঙ। গাছ প্রায় ১২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা কাণ্ডের সাথে বিপরীতমুথীভাবে থাকে। পাতা যৌগিক, পাতার বোঁটা লম্বা। বর্ষাকালে ফুল ফোটে। রাতে ফুল ফোটে ও সকালেই ঝরে যায়। রাতে বাদুড় দ্বারা এ ফুলের পরাগায়ন ঘটে। ডালের আগায় মঞ্জরীদণ্ডে অনেকগুলো ফুল পর্যায়ক্রমে ফোটে, পুষ্পমঞ্জরী রেসিম প্রকৃতির, পুষ্পমঞ্জরী ২৫ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার লম্বা। মঞ্জরীদণ্ডে উর্ধ্বমুখী। ফুল উভলিঙ্গী, ঘণ্টাকৃতি, ঘিয়া রঙের ও পাঁপড়ির কিনারা হালকা বেগুনি। সাদা ফুলও আছে। ফুলের পাঁপড়ি ৫টি খাঁজবিশিষ্ট, পাঁপড়ি প্রায় ১০ সেন্টিমিটার লম্বা। বর্ষাকালের শেষে শরতে কচি ফল পাওয়া যায়। ফল লম্বা ও চ্যাপ্টা, আকৃতি অনেকটা তরবারির মতো, ৪৫ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ২.৫ থেকে ৪ সেন্টিমিটার চওড়া, ফলের খোসা শক্ত, কাঁচা ফলের রঙ সবুজ বা তামাটে, পাকলে খোসা কালো বা গাঢ় বাদামি হয়ে যায়। একসাথে কয়েকটা ফল ঝুলতে থাকে। বীজ গোলাকার বা উপবৃত্তাকার, স্বচ্ছ। খনাগুলার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ওরোজাইলাম ইন্ডিকাম (Oroxylum indicum) ও গোত্র বিগ্নোনিয়েসী।
শোনা গাছের ব্যবহার বহুমূখী। শোনা একটি বুনো সবজি ও ভেষজ গাছ। সাধারণত পাহাড়ের বনে জঙ্গলে শোনা গাছ জন্মে। পাহাড়ে জুমের জমিতে মাঝে মাঝে কিছু শোনা গাছ দেখা যায়। লম্বা ও চ্যাপ্টা তলোয়ারের মতো কচি ফল পাহাড়িরা সবজির মতো রান্না করে খায়। চট্টগ্রামের লোকেরা শোনার কচি ফল আগুনে ঝলসে নিয়ে ওপরের পাতলা খোসা ফেলে কুচি কুচি করে কেটে ধুয়ে ভাজি করে খায়। ভেষজ উপকারের জন্য উপজাতিদের কাছে শোনা গাছ বেশ জনপ্রিয়। এর শিকড়, বাকল, পাতা ইত্যাদি ভেষজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঠ অনেক কাজে লাগে। কাঠ ও বাকল থেকে রঞ্জক বা রঙ পাওয়া যায়। খনাগুলা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়।
পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান পাঁচ উপজাতির প্রায় সব লোকই খনাগুলা খায়। তবে ফল অন্যান্য সবজির মতো রেঁধে খাওয়া হয় না। কাঠ কয়লার আগুনে কচি ফল সেঁকলে বা পোড়ালে ভেতরের শাঁস গলে নরম মাখনের মতো হয়ে যায়। এই শাঁস চামচ দিয়ে কুড়ে কুড়ে খাওয়া হয়। এ গাছের বাকল চূর্ণ জন্ডিস রোগ সারানোর জন্য চাকমারা ব্যবহার করেন। মারমারা শিকড়ের রস দেহের ব্যাথা-বেদনা দূর করতে ও চাকমারা বাকলের রস জন্ডিস ও ডায়াবেটিস রোগ সারাতে ব্যবহার করেন। মধুপুরের গারো উপজাতির লোকেরা কাটা ক্ষত সারাতে বাকলের রস লাগান। এ গাছের ছাল বলকারক, বেদনানাশক, ধারক ও পরিপাকশক্তি বর্ধক। বাতরোগীদের এ গাছের ছালের ক্বাথ দিয়ে স্নান করানো হয়। হলুদের সাথে ছাল বেটে প্রলেপ দিলে গরুর ঘাড়ের ঘা ও ফোলা সেরে যায়। কোথাও মচকে গেলে ও ঘা হলে বাকল বেটে সেখানে লাগিয়ে দিলে উপকার হয়। যে কোনও ফোলায় খনাগুলা গাছের ছাল বেটে অল্প গরম করে সে অবস্থায় প্রলেপ দিলে ফোলা সেরে যায়। বাকল চূর্ণ হাঁপানি রোগীর জন্য উপকারী। শিকড়ের রস তিল তেলের সাথে গরম করে কানে দিলে কানপাকা ও কানের পুঁজ সেরে যায়। শোনার ছাল বাটা দিয়ে তৈরি তেল তুলি দিয়ে রোজ একবার কানে লাগালে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়।
কেউ কেউ এ গাছ বাগানে, উদ্যানে, রাস্তার ধারে শোভাবর্ধক গাছ হিসেবে লাগান। কাঠের ব্যবহারও আছে। কাঠ ধূপের মতো পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে ঘরের মশামাছি কমে যায়। কোনও কোনও দেশে এ গাছের পাতা ও কাণ্ড খাওয়া হয়। থাইল্যান্ড ও লাওসে এর কচি ফল খাওয়া হয়। ফলের শাঁস তিতা। দুই রকমের শোনা ফল রাঙ্গামাটিতে দেখেছি। এক রকমের কচি শোনা ফলের রঙ সবুজ, অন্যটার রঙ তামাটে সবুজ। তামাটে সবুজ রঙের ফলের শাঁস তিতা, সবুজটা তিতা না।

সাধারণত শোনা গাছ কেউ চাষ করে না, জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে। বয়স্ক ডাল কেটে বা কাটিং করে পুঁতে দিলেও গাছ হয়। ফল পাকলে ফেটে যায়। পাকা ফলের বীজ সংগ্রহ করে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে মাটিতে বা পলিব্যাগের মাটিতে পুঁতে দিলে চারা গজায়। উপজাতিদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, বীজ ভালোভাবে রাখতে পারলে ৩ বছরের পুরনো বীজও গজায়।
মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের ভেতরে ক্যাকটাস হাউসের পাশে কয়েকটা শোনা গাছ আছে। এ গাছ বলধা উদ্যানেও আছে। এক সময় রমনা থানার উত্তরে ইস্পাহানী কলোনীর কাছে রাস্তার পাশে একটি শোনা গাছ ছিল বলে নিসর্গী বিপ্রদাশ বড়ুয়া তাঁর ‘গাছপালা তরুলতা’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে সে গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে।
চালতা
কবি জীবনানন্দ দাশের ‘সেইদিন এই মাঠ’ কবিতার মতো চালতা ফুল হেমন্তের শিশিরে না ভিজলেও সে সময় পাওয়া যায় চালতা ফলের দেখা। এ পৃথিবীতে আমরা না থাকলেও চালতা গাছে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে, চালতার ঘন পত্রপল্লবের আঁধারমাখা ছায়ায় বসে লক্ষ্মীপ্যাঁচা অপেক্ষা করবে তার সাথীটির জন্য:
‘‘আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে আর কবে ঝরে?’’

চালতা ফুলের অসাধারণ শুভ্র রূপের সাথে যাদের পরিচয় নেই তারা ঠিক বুঝবে না তার সৌন্দর্য। চালতা ফুলের পাঁপড়িকে কেউ কেউ তুলনা করেন সাদৃশ্যের কারণে ম্যাগনোলিয়া ফুলের পাঁপড়ির সাথে। ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো তার অত সৌরভ নেই ঠিকই, কিন্তু একটা হালকা কি যেন মাদকতাময় ঘ্রাণ পাওয়া যায় সেসব ফোটা ফুল থেকে। তবে সে রূপ দেখতে হলে যেতে হবে সকাল সকাল, না হলে ফুল থেকে খসে পড়বে পাঁপড়িদলগুলো। অবশ্য পাঁপড়িখসা বৃতি আর কেশরেরও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে।
এ দেশে চালিতা, চালতা, চাইলতে ইত্যাদি নামে পরিচিত। চালতার ইংরেজি নাম এলিফ্যান্ট আপেল। ফল বা চালতা ফলগুলো পাতার আড়ালে ঝুলতে থাকে আপেলের মতোই, তবে আপেলের সাথে চালতা ফলের পার্থক্য অনেক। চালতার যে ফল আমরা দেখি, সেটি কয়েকটা পুরুষ্ট বৃতিতে মোড়ানো, প্রকৃত ফলের মতো না। চালতা এ দেশের প্রায় সব জায়গাতেই জন্মে। খুব সাধারণ গাছ। শোভাবর্ধক তরু হিসেবেও কোনও কোনও উদ্যানে লাগানো হয়। ঢাকার বলধা গার্ডেনের শঙ্খনিধি পুকুর ঘাটে লাগানো গাছটিও ফল নয়, শোভা বর্ধনের জন্য লাগানো।
চালতা এদেশে একটি অনাদৃত ফল। ফল দেখতেও আকর্ষণীয় নয়। তবে ফল টক বলে চালতার আচার, চাটনি, টক ডাল অনেকের কাছে বেশ প্রিয়। পাকা ফল থেঁতো করে নুন লংকা দিয়ে মাখলে তা বেশ লোভনীয় হয়। চালতার গাছ ও ফল দেখতে সুন্দর বলে অনেক উদ্যানে এ গাছটি বাহারি গাছের মর্যাদা পেয়েছে। তবে গ্রামে জন্মে সাধারণতঃ জঙ্গলে, কখনও কখনও দু’একটি গাছ বাড়িতে দেখা যায়। ঢাকা শহরে ষাটের দশকে পল্টন ও তেজগাঁওয়ে বেশ কিছু চালতা গাছ ছিল বলে জানিয়েছেন দ্বিজেন শর্মা। গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে ৩৯ নম্বর রোডের ধারে একটি চালতা গাছ আছে। রমনা উদ্যানের ভেতরে ঝিলের পশ্চিম পাশে ও উত্তরে দুটি চালতা গাছ আছে।

চালতার জন্ম ভারতবর্ষে। চালতা গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ডিলেনিয়া ইন্ডিকা (Dillenia indica), গোত্র ডিলেনিয়েসী। চালতা গাছ মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। উচ্চতায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। গাছের গায়ে লালচে রঙের চকচকে বাকল থাকে। পাতার কিনারা খাঁজ কাটা, শিরা উঁচু সমান্তরাল। চালতার ফুল দেখতে খুব সুন্দর। সাদা রঙের। ফুলে পাঁচটি মোটা পাঁপড়ি ও বৃতি সেসব পাঁপড়িকে ঘিরে রাখে। ফুল সুগন্ধযুক্ত। ফুলের ব্যাস ১৫ থেকে ১৮ সেন্টিমিটার। মে-জুন মাসে ফুল ফোটে। চালতা ফলের যে অংশ খাওয়া হয় তা আসলে বৃতি। প্রকৃত ফল বৃতির আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ফল বাঁকানো নলের মতো, ভিতরে চটচটে আঠার মধ্যে থাকে বীজ। চালতার ফল কখনো খাওয়া যায় না। মাংসল বৃতিই খেতে হয়। বর্ষার পর শরৎ থেকে ফল পাকতে শুরু করে, হেমন্তে বেশি ফল পাওয়া যায়। শীতকালেও কোনও কোনও গাছে ফল থাকে।
পাকা চালতার রস চিনি দিয়ে খেলে সর্দি জ্বরে উপকার হয়। কচি চালতা বাত ও পিত্তনাশক। বীজ থেকে চারা তৈরি করা যায়। গাছে ফল পাকলে যদি তা না পাড়া হয় তবে সে ফল থেকে বীজ আপনা আপনি মাটিতে ঝরে পড়ে ও প্রাকৃতিকভাবে চারা গজায়। এজন্য চালতা তলায় অনেক সময় ছোট ছোট অনেক চারা দেখা যায়। এসব চারা তুলে লাগালেও গাছ হয়। তবে বীজ থেকে করা চারার গাছে ফল ধরতে ৬ থেকে ৭ বছর লেগে যায়। গাছ বাঁচে ২৫ থেকে ৩০ বছর। শাখা কলম বা কাটিং করেও চালতার চারা তৈরি করা যায়। সেসব কলমে দ্রুত ফুল-ফল ধরে।

খিরনি
খিরনি আমাদের খুব পরিচিত বৃক্ষ না, কিন্তু নার্সারির মালীদের কাছে এ গাছটি খুব পরিচিত ও তার কদরও রয়েছে। খিরনি গাছের চারা না হলে তাঁরা সফেদার জোড়কলম করতে পারেন না। এজন্য খিরনির বীজ পাওয়ার জন্য তাঁদের খুঁজতে হয় খিরনি বা খিরকেজুরের গাছ।

খিরনি আমাদের এ উপমহাদেশেরই গাছ, সে অর্থে এটি আমাদের দেশি গাছ। এ গাছের সংস্কৃত ও হিন্দি নামও খিরনি। খিরনির ইংরেজি নাম সিলোন উড (Ceylon Ironwood) বা রায়ান ট্রি (Rayan Tree)। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ম্যানিলকারা হেক্সান্ড্রা (Manikara hexandra) ও গোত্র স্যাপোটেসী (Sapotaceae)। খিরনি বৃহৎ আকারের চিরসবুজ গাছ। গাছের বৃদ্ধি খুব ধীর। গাছ ১২ থেকে ১৫ মিটার লম্বা হয়। বাকল ধূসর ও খসখসে। গাছের মাথায় ডালপালা বেশ প্রসারিত ও ঘন, বাকল আঁচড়ালে সেখান থেকে খিরের মতো সাদা আঠা ঝরে। পাতা সরল, ডালের মাথায় গুচ্ছাকারে জন্মে। ফুল খুব ছোট, হালকা হলদে রঙের। ফল দেখতে অনেকটা দেশি বনখেজুরের ফলের মতো আকৃতির। এজন্য এ গাছের এক নাম খিরখেজুর। ফল রসালো ও পাকলে উজ্জ্বল হলুদ রঙের হয়, পাকা ফল টাটকা ও শুকিয়ে খাওয়া যায়, স্বাদে মিষ্টি ও অম্লীয়। পাকা ফল থেকে সুষ্টি ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কাঠ খুব শক্ত, ভারী নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হয়। শ্রাবণে ফুল ফোটে, অগ্রহায়ণে ফল পাকা শুরু হয়। বীজ পিষে খিরনির তেল পাওয়া যায়, তেল হলকা হলদে রঙের। এই তেল বাজারে ‘রায়ান তেল’ নামে পরিচিত। বীজের শাঁসে প্রায় ২৫ শতাংশই তেল থাকে। বীজ ও বাকলের ভেষজ গুণ আছে। বীজ থেকে চারা হয়। চারা লাগানোর তিন বছর পর থেকে সেসব গাছে ফুল ও ফল ধরা শুরু হয়।

খিরনি একটি দুর্লভ বৃক্ষ, খুব কম দেখা যায়। ঢাকা শহরে চামড়া প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে একটি খিরনি গাছ আছে। রমনা উদ্যানে যে খিরনি গাছটি আছে সেটি আসলে খিরনির নিকট আত্মীয়, যার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ম্যানিলকারা কাউকী (Manilkara Kaukii)।

বোতলব্রাশ
বোতলব্রাশ ফুলের পুষ্পমঞ্জরী ঝুলতে থাকে যা দেখতে হবহু বোতল পরিষ্কার করার ব্রাশের মতো। তাই এর ইংরেজি নাম বোতলব্রাশ। প্রায় ১২ সেন্টিমিটার লম্বা পুষ্পমঞ্জরীতে অসংখ্য লাল রঙের ফুল ঘনভাবে ফোটে। এর ফুল ফোটে শরত-হেমন্তে। শাখা-প্রশাখার অগ্রপ্রান্তে ফুলগুলো ফোটে। ক্ষুদ্রাকৃতি ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ি। অসংখ্য লাল কেশরের মাথায় গুড়ো গুড়ো হলুদ বিন্দুর মতো পরাগরেণু লেগে থাকে। পুষ্পমঞ্জরী প্রায় চোঙের মতো। গাছ বৃক্ষ প্রকৃতির, ঝোপাল ও মধ্যমাকৃতির। গাছের উচ্চতা ১২ মিটার পর্যন্ত হয়। ডালপালা কিছু থাকে উর্ধ্বমুখে, কিছু থাকে ভূমির দিকে। তবে চিকন চিকন পাতাসহ শাখা-প্রশাখার দোলানো ডগা দেখতে খুবই সুন্দর। গাছের বাকল অমসৃণ ও ফাটা ফাটা।

সারা বিশ্বে বোতলব্রাশের প্রায় ৩০টি প্রজাতি আছে। তবে সেগুলো এদেশে নেই। লাল ফুলের বোতলব্রাশ এ দেশে সচরাচর দেখা যায় যার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Callistemon citrinus ও পরিবার মির্টেসী। হালকা হলুদ ফুলের প্রজাতি Callistemon pollidus, এটিও আছে এদেশে, তবে খুব কম চোখে পড়ে। সম্প্রতি সাদা রঙের ফুল ফোটা আর এক প্রজাতির বোতলব্রাশ গাছ এ দেশে এসেছে যার নাম উইলো বোতলব্রাশ। এ গাছের পাতাগুলো খুবই ছোট, সরু ও লম্বা, ঘন, পাতা ডললে লেবুর মতো ঘ্রাণ পাওয়া যায়, কচি পাতা লালচে। উইলো বোতলব্রাশের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Callistemon salignus। এ গাছ লাল বোতলব্রাশ গাছের মতো বড় বৃক্ষ হয় না, গুল্মের মতো ঝোপ করে থাকে, ডালপালাগুলো সরু, ফুল ফোটে বসন্ত-গ্রীষ্মে। এই গাছ খরা ও জলমগ্নতা সইতে পারে।

মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে আন্তর্জাতিক বাগান সেকশনের কাছে উইলো বোতলব্রাশের একটি সুন্দর ঝোপ রয়েছে। নগর উদ্যানে, লেকের ধারে, বাগান পথের দুধারে বোতলব্রাশ মানানসই। ঢাকার চন্দ্রিমা উদ্যানে ক্রিসেন্ট লেকের পাড় ধরে লাগানো বোতল ব্রাশের গাছগুলো খুবই শোভনীয়। ঢাকা শহরে থাকা পুরনো বোতলব্রাশ গাছগুলোর মধ্যে এগুলো অন্যতম। ঢাকা শহরে আর কোথাও এতগুলো বোতলব্রাশ গাছ নেই। রমনা উদ্যানের ভেতরে কয়েকটা বয়স্ক বড় বোতলব্রাশ গাছ আছে। বোতলব্রাশ গাছের উৎপত্তি অস্ট্রেলিয়ায়।
বকফুল
বকফুল শিম বা মটর গোত্রীয় গাছ। কিন্তু গাছ দেখতে মোটেই শিম বা মটরের মতো নয়। ফুলের গড়নে কিছুটা মিল থাকলেও পাতা ও গাছের সাথে মিল নেই। ধৈঞ্চা গাছের সাথে কিছুটা মিল আছে। তবে বকফুলের গাছ ধৈঞ্চার চেয়ে অনেক বড় ও মজবুত। গাছ অতিদ্রুত বাড়ে, মাত্র ৫ থেকে ৬ মাস বয়সেই গাছ প্রায় ২ থেকে ৩ মিটার লম্বা হলে ফুল দিতে শুরু করে। লাগানোর প্রায় ৯ মাস পর ফল পাকে ও বীজ হয়। এ গাছের অনেকগুলো বাংলা নাম— বক, বকে, বগ, বকফুল, বগফুল, অগস্তা, অগাতি ইত্যাদি। তবে গাছটি এ দেশে বকফুল নামেই বেশি পরিচিত। ইংরেজি নাম Hummingbird tree, উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম সেসবানিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা (Sesbania grandiflora), গোত্র ফ্যাবেসী (Fabaceae)।

ফুলের রঙ বকের মতো সাদা ও বকের গলার মতো বাঁকা বলেই হয়ত নাম হয়েছে বকফুল। কিন্তু এখন এর অনেক নতুন জাত এসেছে যেসব জাতের ফুলের রঙ সাদা নয়। এদেশে ৩ রঙের বকফুল দেখা যায়— সাদা, লাল ও গোলাপি। লাল ফুলের জাতটি এ দেশে এসেছে থাইল্যান্ড থেকে। সেজন্য একে অনেকে বলেন ‘থাই বকফুল’। অনেকে সৌন্দর্যের জন্যও এ জাতটি বাড়িতে ও উদ্যানে লাগান।
বিভিন্ন দেশে বকফুল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। সাধারণত: না ফোটা বকফুল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। সবজি ছাড়া পশুখাদ্য হিসেবেও বকফুল গাছের ব্যবহার রয়েছে। ধৈঞ্চার মতো বকফুল গাছ ধানের জমিতে সবুজ সার ফসল হিসেবেও চাষ করা যায়। কেননা এ গাছের শিকড় বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চয় করে মাটিতে যোগ করে, ফলে জমির উর্বরতা বাড়ে। তাছাড়া কচি পাতা ও ডালপালা চাষ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ হয়। গাছ পুরনো হরে কেটে তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে পোড়ানোর সময় ধোঁয়া হয় বলে অনেকে বকফুল কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন না। আসবাবপত্র বা গৃহনির্মাণে এর কোনও দারুমূল্য নেই। কেননা এর কাঠ নরম ও কিছুদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। বকফুল গাছের কিছু ভেষজগুণও আছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বকফুল গাছের প্রতিটি অংশই ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। জ্বর, ফোলা ও ব্যাথাবেদনা সারাতে এ গাছের মূল ব্যবহার করা হয়। বাতের ব্যথায় শিকড় চূর্ণ জলের সাথে গুলে ব্যাথা জায়গায় ঘষলে, লাগালে বা প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। বাকল বসন্ত রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগে। ফিলিপাইনে গাছের বাকল মুখের আলসার সারাতে ব্যবহার করা হয়। চুলকানি-পাঁচড়া সারাতে কম্বোডিয়ায় বাকল চূর্ণ লাগানো হয়। কৃমি ও জ্বর সারাতে পাতার রস খাওয়ানো হয়।

বকফুল গাছের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (মালয়েশিয়া, ফিলিপিন, ব্রুনাই) থেকে উত্তর অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বকফুল গাছ জন্মে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, লাওস, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চীন, ফিলিপিন, ভারত প্রভৃতি দেশে বকফুল গাছ লাগানো হয়। এ গাছটি এখন অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও জন্মাচ্ছে। বিগত প্রায় দেড়শ বছর ধরে পশ্চিম আফ্রিকাতেও বকফুলের চাষ করা হচ্ছে।
বকফুল গাছ ছোট বৃক্ষ প্রকৃতির। গাছ ৩-৮ মিটার লম্বা হয়। কাঠ নরম। পাতা দেখতে ধৈঞ্চা বা তেঁতুল পাতার মতো, পাতার ডাটির দুপাশে ছোট ছোট পাতা চিরুণির মতো সাজানো থাকে। পাতার অগ্রভাগ সূঁচালো নয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গাছে ফুল ফোটে। বকফুলের আয়ুর্বেদিক নাম ‘অগস্ত্য’। ফুলের গড়ন অনেকটা বকফুলের গলার মতো বা কাস্তের মতো। চার রকম ফুল দেখা যায়। ফুলের রঙের ওপর ভিত্তি করে চার রকম বকফুলের নামকরণ করা হয়েছে ‘শ্বেত অগস্ত্য’ (সাদা ফুল), ‘পূত অগস্ত্য’ (হলুদ ফুল), ‘নীল অগস্ত্য’ (নীল ফুল) ও ‘লোহিত অগস্ত্য’ (লাল ফুল)। ফুল থেকে বরবটি শিমের মতো ফল হয়। কাঁচা ফলের রঙ সবুজ, পাকলে হলুদ পরে শুকিয়ে বাদামি হয়ে যায়। ফলের মধ্যে বরবটি বীজের মতো বীজ হয়। ফল প্রায় ১ ফুট বা ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। একটি ফলের ভেতরে ১৫-৩০ টি বীজ থাকে। বীজ থেকে চারা হয়।

বীজ থেকে সহজে চারা হয়। শরৎ-হেমন্তে ফোটা ফুলের বীজ হয় বসন্তে। তখন বীজতলায় বীজ বুনে চারা তৈরি করা যায়। বীজ গাছ থেকে সংগ্রহের পর দ্রুত বীজ সজীবতা হারাতে থাকে। তাই সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজ মাটিতে বুনে দেয়া ভালো। গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল চারা লাগাানোর ভাল সময়। আষাঢ় মাসে লাগানো গাছে ঠিকমত যত্ন নিলে কার্তিক মাস থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করে। বীজ ছাড়া বয়স্ক ডাল কেটে লাগালে তা বেঁচে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের উদ্ভিদ উদ্যানের প্রবেশ পথের ডানপাশে একটি বকফুল গাছ আছে।
গাছ চিনতে গাছের কাছে
আধুনিক উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তার ভিত্তি রচনা করেন সুইডেনের অধিবাসী কার্ল লিনিয়াস। ১৭৩২ সাল, কার্ল লিনিয়াসের বয়স তখন ২৭ বছর। গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য রয়্যাল সোসাইটি অব সায়েন্স তাঁকে ৫০ ডলার স্কলারশিপ দিয়েছিলেন। কার্ল লিনিয়াস সেই স্কলারশিপ পাওয়ার পর তা দিয়ে ৫ মাসের জন্য ল্যাপল্যান্ড ভ্রমণে যান। উদ্ভিদ সংগ্রহের সেই অভিযানে লিনিয়াস প্রায় ১০০০ মাইল (১৬০০ কিলোমিটার) পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের ফলে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘ফ্লোরা ল্যাপোনিকা’। আজ আমরা গাছপালার দুটি অংশ সম্বলিত যে উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিখি সেই নামকরণ ও শ্রেণিবিন্যাস তিনি করে গেছেন। কথায় বলে, দশটা বই পড়ে যা জানা যায় না, দশ মাইল হেঁটে যাওয়ার সময় দুচোখে যা পড়ে তা কেউ পর্যবেক্ষণ করলে (তাকানো না) তার চেয়ে বেশি জানা যায়। গাছপালা নিয়ে লিখতে গিয়ে তাই আমি গাছের কাছেই যাই। গাছকে পর্যবেক্ষণ করি। ঢাকা শহরের কত জায়গার কত গাছ যে আমি হেঁটে হেঁটে দেখেছি! দেখতে দেখতে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমনি বইয়ে না লেখা অনেক কথাই গাছের কাছে গিয়ে জানতে পেরেছি। উপলব্ধি করেছি, যদি সত্যি সত্যি কেউ গাছপালা চিনতে চায়, গাছের কথা জানতে চায়, তাহলে তাকে গাছের কাছেই যেতে হবে। সেসব গাছকে নানা সময়ে দেখার চেয়ে ওদের চেনার আর কোনও ভালো উপায় আছে বলে আমার মনে হয় না।
লেখক: কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক।
ইমেইল: kbdmrityun@gmail.com