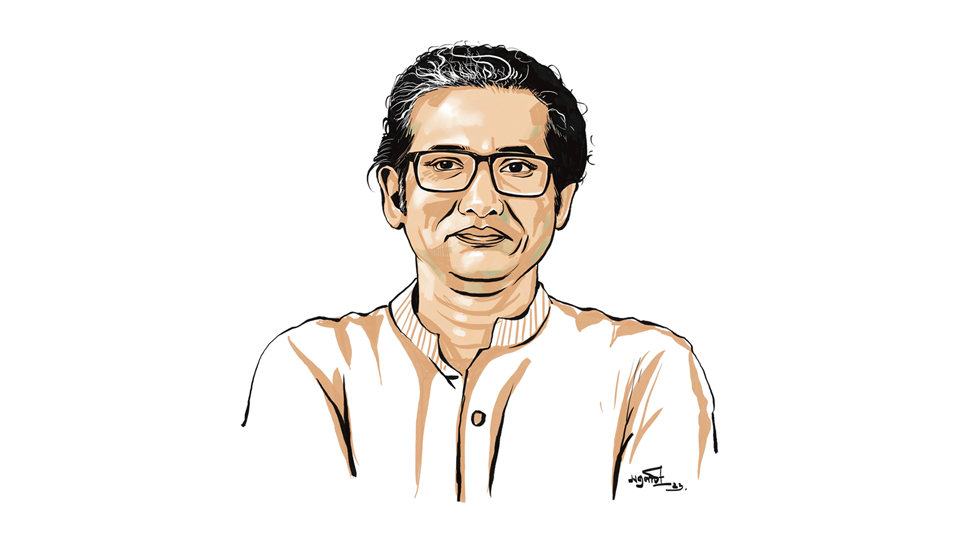কেউই অস্বীকার করবেন না, মানুষের পড়ার অভ্যাস কমে গেছে, পত্রিকাগুলোর সার্কুলেশন ক্রমাগত কমছে, ছাপা বইয়ের বাজার মন্দা। মানুষ আর বই পড়তে চায় না— ছোটখাটো, হালকা ও চটুল লেখা হয়ত চটজলদি পড়ে ফেলে, কিন্তু বড় লেখা, চিন্তা উদ্রেককারী সিরিয়াস লেখার ধারেকাছেও ভিড়তে চায় না। অথচ এককালে ওই প্রবচন তো আমাদের মুখস্ত থাকত— ‘‘লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে’’। ফলে, গাড়িঘোড়া চড়ার প্রলোভনে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত পরিবারে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় বিশেষ নজর দেওয়া হতো। ভদ্রলোক হওয়ার বাসনা তাড়িত করত সবাইকে। ভদ্রলোকদের গেরস্থালিও ছিল দেখবার মতো। সকালের নাস্তার টেবিলে টাটকা দৈনিক পত্রিকা, চায়ের কাপ হাতে পরিবারের কর্তা পাতা উল্টাচ্ছেন, পরিবারের অন্যরা অপেক্ষায় থাকছেন কর্তার পড়া শেষ হওয়া মাত্র তারাও পড়তে শুরু করবেন বলে! আর বসার ঘরে টেবিলের পাশে বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক; দেয়ালের একপাশে হয়ত কয়েকটা বুকশেলফ। গ্রামে গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলার নানা উদ্যোগ, আর স্কুল-কলেজের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় বই উপহার, এমনকি তরুণ তরুণীদের প্রেম নিবেদনেও— হয়ত পূর্ণেন্দু পত্রীর কোনও বই, জয় গোস্বামী, কিংবা হেলাল হাফিজের ‘যে জলে আগুন জ্বলে’! আধুনিক নাটকে, সিনেমায়, উপন্যাসে, গল্পে এরকম দৃশ্য বারবার নির্মিতও হয়েছে। পড়ালেখা করে ইউরোপীয় ভাবধারায় আধুনিক হয়ে ওঠার এক প্রবল বাসনা আমাদের তাড়িত করত!
কিন্তু ডাকপিয়নের চিঠি আজ কেবলই এক নস্টালজিয়া! সময় কত বদলে গেছে, মাত্র কুড়ি-ত্রিশ বছরে! পার্কে যান, হাটে-বাজারে, রাস্তায়, স্কুল-কলেজে, রেলে-বাসে, কিংবা কোনও পরিবারের অন্দরমহলে, টেবিলের চারপাশজুড়ে আড্ডায়। বই, পত্র-পত্রিকা আর চোখে পড়বে না, বরং দেখবেন ক্ষুদে শিশুকিশোর থেকে বৃদ্ধ সকলেই এক অদ্ভুত যন্ত্র হাতে ঘুরছে কিংবা ঘাড় বাঁকিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে— সেটা স্মার্ট ফোন। মানুষের জীবন আজ ঢুকে গেছে স্মার্ট ফোনে। সেই ফোনে কিংবা ট্যাবে বা ল্যাপটপে তারা কিছু দেখে, কিংবা স্মার্ট টেলিভিশনে দেখে। হয়ত এসব মাধ্যমেও কিছু পড়তে হয়, কিন্তু প্রধানত তারা দেখে। স্ক্রিনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকাই তো একটা দেখা— কারণ সেই স্ক্রিনের আলো এসে ঠিকরে পড়ে চোখেমুখে। স্ক্রিনজুড়ে লেখা ফুটে ওঠে, সাথে ভিজুয়াল ইমেজ, আর শোনার জন্য থাকে মিউজিক, সাউন্ড ও কথা। সামাজিক মাধ্যমগুলোতে আজ চলছে ভিডিও কনটেন্টের ভরা জোয়ার— শর্ট ভিডিও, ভিডিও রিলস; টিকটক, টুইটার, ইন্সটাগ্রামের ভিডিও ও ইমেজে সবাই বুঁদ হয়ে আছে। মূলধারা প্রিন্টমিডিয়াগুলোও আর আজ কেবল প্রিন্টে সীমিত নয়, বাজারে টিকে থাকতে তাকে বানাতে হয় মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট, এবং হাজির থাকতে হয় অনলাইনের বিভিন্ন প্লাটফর্মে। এমনকি দেখা যাচ্ছে, দৈনিক পত্রিকার প্রিন্ট সংস্করণের চেয়ে কোনও প্রত্যন্ত গাঁয়ের ইউটিউবারের সাবস্ক্রাইবার বা ভোক্তা বেশি! সেইসাথে অষ্টপ্রহর টিভি আর অনলাইনের নানা আয়োজন তো আছেই। অনেকে বলেন, এটা দেখা ও দেখানোর সময়, দেখনদারির সময়। তাত্ত্বিকরা সেই ১৯৯০-এর দশকেই এসে বলে দিয়েছেন— সমাজ এক পিক্টোরিয়াল টার্ন বা ভিজুয়ালের বা ছবির বাঁকে এসে দাঁড়িছে। এটা ভিজুয়ালের সময়, ভিডিওর সময়, আরও বলা হচ্ছে ভিডিওই ভবিষ্যৎ!
কিন্তু সেটা কেমন ভবিষ্যৎ হবে? আমরা কি লেখাপড়া বাদ দিয়ে দেখতে দেখতে, দেখাতে দেখাতে নিরক্ষর রয়ে যাবো? নাকি পড়ালেখার যুগ অতিক্রম করে অন্য কোনও ভবিষ্যতের দিকে আমরা ধাবমান? কিন্তু তারই বা মানে কি! কীভাবে আমরা এ সময়ে এসে পৌঁছালাম? লেখা, পড়া ও দেখার কালচারের ইতিহাস কি? আর সে ইতিহাসের সাথে আমাদের সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্রের রূপান্তরের সম্পর্ক কী? কী সম্পর্ক আমাদের অনুভূতি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশ্ববীক্ষা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার? আমার এ আলোচনা এক লম্বা সফরের গল্প বটে— তবে সংক্ষেপেই সে গল্প বলব। অক্ষরহীন সমাজ থেকে লেখাপড়ার সমাজ, ইলেক্ট্র্রনিক মিডিয়া হয়ে, এনালগ সম্মুখে ধাবমান ঘড়ির টাইম পেরিয়ে, ডিজিটাল ও নেটওয়ার্কের তাৎক্ষণিক টাইমে এসে আমরা ভাবতে বসেছি— কোথায় এসে দাঁড়ালাম! সমাজের গতিমুখ আজ কোন দিকে ফেরানো?
২. প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে হোমাসেপিয়ান্স বা আজকের মানুষের পূর্বপ্রজন্মের দেখা পাওয়া যায় আফ্রিকায়। অন্যান্য পশুপ্রাণীর মতোই, তাদেরই পাশে পাশে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে তারা দলবেঁধে ফিরত। প্রত্নবিশারদ ও জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলছেন মাত্র ৭০ হাজার বছর আগে লোহিত সাগর উপকূলে মেসোপটেমিয়া বা ইরান-ইরাক এলাকায় প্রথম তারা সফলভাবে টিকে যায় এবং তারপরে থিতু হয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তারপরে নদীর জল অনেক গড়িয়েছে। এই মেসোপটেমিয়া এলাকায় কৃষিসভ্যতা গড়ে ওঠে মাত্র পনের-কুড়ি হাজার বছর আগে, আর এ জনগোষ্ঠীই মাত্র পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে হিসেব-নিকেশ রক্ষার স্বার্থে লেখার উদ্ভাবন করে— তবে সে লেখা ছিল কেবলই স্মৃতির সহায়ক এক অবলম্বন। পশ্চিমের ইতিহাস বলছে, পিক্টোগ্রাম, ইডিওগ্রামে লেখার পর্ব পেরিয়ে আরও কিছুকাল পরে সেমেটিক জনগোষ্ঠী বর্ণমালা উদ্ভাবন করে খ্রিস্টের জন্মের ১৫০০ বছর আগে। কিন্তু সে বর্ণমালায় কোনও স্বরধ্বনি ছিল না। একটা ভাষাকে বর্ণমালায় ধরতে পারার কৃতিত্ব দিতে হবে গ্রিকদেরকেই। খ্রিস্টের জন্মের মাত্র ৪০০ বছর আছে গ্রিকরা প্রথম আবিষ্কার করে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিসহ এক পূর্ণাঙ্গ বর্ণমালা। বলা যেতে পারে, এ পৃথিবীতে লেখা ও পড়া তখন থেকেই একটা সিস্টেম হিসেবে দাঁড়াতে থাকে।
সেই সময় থেকেই পড়ালেখার একটা চর্চা আমরা গ্রিসে শুরু হতে দেখি। যদিও, লিখতে ও পড়তে পারা মানুষ ছিল হাতে গোনা। আর লেখার জন্য পেপার বা প্যাপিরাসের দেখা তখনও পাওয়া যায়নি। পাথর, মাটির ফলক, গাছের বাকল বা চামড়ার উপরে লেখা হতো। আর বই হলে তা শ্রমসাধ্য উপায়ে হাতে লিখেই কপি করতে হতো— ভুলভালও থেকে যেত বিস্তর। তবে, প্লেটো কিন্তু লেখাকে ভালো চোখে দেখেননি, যদিও তিনি লিখেই বলেছেন সেসব কথা। আর বলাই বাহুল্য, লেখার প্রভাব সমজে পড়তে শুরু করেছিল বলেই লেখার সমালোচনায় তিনি উদ্যমী হয়েছিলেন। অনেকে বলেন, তিনি রক্ষণশীল দার্শনিক ছিলেন। প্লেটো মনে করতেন মুখের জবানের চেয়ে লেখা রেপ্রিজেন্টেশনের দুর্বল মাধ্যম। কথা সরাসরি আমাদের আত্মা থেকে বেরিয়ে আসে, একটা জীবন্ত ব্যাপার। কিন্তু লেখা রক্তমাংসের মানুষের জীবনের বাইরে এক ধরনের বহিস্থ ও স্বাধীন অস্তিত্ব তৈরি করে। কথা প্রাকৃতিক, কিন্তু লেখা কৃত্রিম, প্রাকৃতিকভাবে লেখার কোনও উপায় নাই। লেখা নিজেকে নিজে ডিফেন্ড করতে পারে না, কথাও কইতে পারে না। বই প্রাণহীন, একটা মৃত বস্তু। মুখের কথা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে এবং তার একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার আছে, কিন্তু লেখা তা পারে না। সর্বোপারি, তার অভিযোগ, লেখা ও পড়া মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে দেয়। অথচ অবাক বিষয়, প্লেটোই এ জগতের প্রথম লাইব্রেরিও গড়ে তুলেছিলেন!
সে যাই হোক, কথ্য ঐতিহ্য বা অক্ষরহীন সমাজ থেকে, অর্থাৎ কথার ঐতিহ্য থেকে লেখার ঐতিহ্যে আসা এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করে মানুষের চৈতন্য ও অভ্যাসের জগতে। আদিম সমাজে কথার ঐতিহ্য ছিল স্মৃতিবিহীন, ইতিহাসবিহীন, তার সময় চক্রাকারে ঘোরে কিংবা স্থানু, ক্যালেন্ডার বা ঘড়ি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। তাদের জীবন ছিল বর্তমানকেন্দ্রিক, তাৎক্ষণিকতাই সেখানে মুখ্য, অনেকটা ম্যাজিকাল ও মিথিকাল পরিসরে তারা বাস করত। কিন্তু লেখা একরৈখিক প্রগতির পথের সূচনা করে। লেখাই প্রথমত ইতিহাসচেতনা গড়ে তোলে, লেখার মাধ্যমে অতীতের পুনর্নিমাণ সম্ভব হয়ে ওঠে। গ্রিক ও ল্যটিন ভাষায় এবং তারপরে অন্যান্য ভাষায়ও বর্ণমালা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে লেখা হয়ে ওঠে ‘আধুনিক’ সভ্যতার বাহন। বলা যায়, লেখার প্রযুক্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং এমনকি আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তির বিপ্লব। সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। লেখা ও পড়া শুরু হলেই যে আমরা একটা শিক্ষিত সমাজ পেয়ে গিয়েছি এমন নয়। তার জন্য আমাদেরকে আরও বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত লেখা ও পড়ার চর্চা কেবল ব্যবসাবাণিজ্যের হিসেবনিকেশ রক্ষাকারী আর পুরোহিতদের ধর্মচর্চাতেই বেশি কাজে লাগত। জ্ঞানবিদ্যা-সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চায় তার ব্যবহার ছিল অতি সীমিত। সাধারণ মানুষের তাতে অধিকার ছিল না। লিখতে ও পড়তে পারা এক বিশেষ দক্ষতা হিসেবে গণ্য হতো। লিখিত টেক্সট পড়ে শোনানো হতো শ্রোতাদেরকে। পার্চমেন্ট বা চামড়া, আর এগারো শতকের পরে মিশর থেকে আমদানিকৃত প্যাপিরাস ইউরোপে পড়ালেখার বিস্তার ঘটায়। ইউরোপের রেনেঁসা আর পড়ালেখার অভ্যাস সমান্তরালে এগিয়েছে। কিন্তু পড়ালেখার জগতে সবচেয়ে বড় বিপ্লব নিয়ে আসে ষোল শতকে মূদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার।
৩. ১৫৫০-এর দশকেই গুটেনবার্গ তার প্রেস থেকে বাইবেল প্রকাশ করেন। যদিও এ প্রেস ছিল ধীর গতির, ছিল ব্যয়বহুল, ও প্রাযুক্তিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। মুসলিম বণিকদের মারফতে চীন থেকে তখন কাগজও এসে পড়েছে ইউরোপে! তখন একটা বই ছাপতেই বহুদিন লেগে যেত। এই সময়ে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বেড়ে চলেছিল, আর বেড়ে চলেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন ও সম্পদ লোপাট। ফলে, তথ্যের চাহিদা তখন ক্রমাগত বেড়েছে। এই সময় থেকেই আমরা দেখতে পাই ইউরোপজুড়ে দেশে দেশে প্রিন্টিং প্রেস স্থাপিত হচ্ছে। ল্যাটিন ও গ্রিকভাষার দার্শনিক ও ধর্মীয় বইপুস্তুকের পাশাপাশি বিনোদনের জন্য নানা বইপত্র, ব্লকপ্রিন্টে ছাপা ছবিসহ বই, সংবাদ-বই, বিভিন্ন সাময়িকী ইত্যাদিও প্রকাশিত হতে থাকে। মার্টিন লুথার কিং মূল ল্যাটিন থেকে জার্মানিতে বাইবেল অনুবাদ করে ছাপলেন— ফলে সাধারণ মানুষের নাগালে এল ধর্মের জ্ঞান। কেবল তাই নয়, তিনি প্রবল প্রতাপশালী বিভিন্ন রোমান ক্যাথলিক চার্চের গায়ে ৯৫ টা থিসিস বা সংস্কার প্রস্তাব লিখে চার্চের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। ফলে, ইউরোপে ধর্মীয় আধিপত্যের জগতেও ফাটল ধরে গেল। আর অন্যদিকে, গণিতসহ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন সূত্র নির্ভুলভাবে ছাপা হতে থাকায় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারও ঘটে চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। জ্ঞানের আধিপত্যও ফলে সরে গেল চার্চের হাত থেকে। যদিও গণশিক্ষা ও গণমাধ্যমের যাত্রা আঠার শতকে শিল্পবিপ্লবের পরেই শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, ষোল শতক থেকেই ইউরোপে একটা পড়ুয়া জনগোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে। তারা ভাবতে শেখে, প্রশ্ন করতে শেখে। ফলে দেখা গেল পুরাতন ক্ষমতা-কাঠামো ভেঙে ইউরোপে এক নতুন সমাজের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকরা দাবি করেন, গুটেনবার্গের প্রেসের সুবাদেই ইউরোপ মধ্যযুগের সামন্তসমাজ অতিক্রম করে আধুনিক ও পুঁজিবাদী হয়ে ওঠে। বেনেডিক্ট এন্ডার্সন তার ‘ইমাজিনড কমিউনিটিস’ গ্রন্থে ‘প্রিন্ট ক্যাপিটালিজমের’ কথা বলেন— আদিম ও কৌম সম্প্রদায়বোধ কীভাবে মূদ্রণ সংস্কৃতির প্রভাবে ভেঙে পড়ে তিনি সেই গল্প বলেন। স্বদেশী ভাষার বইপত্র ও পত্রিকা পড়ে মানুষ কীভাবে এক নতুন জাতি কল্পনায় মশগুল হয়, জাতীয়তাবাদ নামের রাজনৈতিক ফর্মেশন ঘটায়, এমনকি আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গড়ে তোলে তিনি তার কথা বলেন। এটা পুঁজিবাদেরও বিকাশের সময়।
৪. আজ আমরা যখন বই পড়া ও শিক্ষার কথা বলি, তার ইতিহাসের আদিসূত্রগুলো আসলে লুকিয়ে আছে ইউরোপের ওই সময়ে। বিভিন্ন দেশের গণসমাজের স্তরে বই-কালচার গড়ে উঠেছে আরও পরে, মাত্র গত ২০০ বছরে। বই পড়া ও শিক্ষা চর্চার সাথে একদিকে যেমন জড়িয়ে আছে নতুন সমাজব্যবস্থা, আধুনিক রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নীতিনৈতিকতা; তেমনই জড়িয়ে আছে ব্যক্তির মানস গড়নেরও সম্পর্ক। এক কথায় আমরা বলতে পারি, বই পড়ার সংস্কৃতি ইউরোপে উদারনৈতিক ভাবধারার সূচনা করে। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের চর্চা, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা গড়ে ওঠা, শিল্পসাহিত্য আর দর্শনের চর্চা ইহজাগতিকতা ও সেকুলারবাদকে উৎসাহিত করে এবং আধুনিকতা এক আধিপত্যশীল ধারণা হিসেবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা বলা যায় ইউরোপের স্থানিক অভিজ্ঞতাকে বাইরের পৃথিবীতে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বই ও মুদ্রণের সংস্কৃতি যে কেবল সমাজ রাষ্ট্র অর্থনীতির খোল-নলচে বদলে দিল তাই নয়, আরও বড় রূপান্তর নিয়ে এল মানুষের চৈতন্যের জগতে—
বলতে গেলে পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে দিল। আগে বই বস্তুটা পড়ার চেয়ে বেশি ছিল শোনার বিষয়, শ্রোতার সামনে পড়ে শোনানো হতো। কিন্তু এই সময় থেকে দেখা গেল, বই-পত্রপত্রিকা মানুষ একান্তে একা একা পড়তে শুরু করেছে। ব্যাক্তিবাদের শেকড় হয়ত কিছুটা প্রোথিত আছে পড়ার অভ্যাসের মধ্যেও। এই যেমন কবিতাও লেখা হতো মঞ্চে পরিবেশনার জন্য। কিন্তু আধুনিক কবিতা হয়ে উঠল একান্তে অভিনিবেশের বিষয়, পড়ে অনুভব করার বিষয়। পড়ার এই ধরন মানুষের চিন্তার ধরনকেও বদলে দেয়, প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত হয়ে সে চিন্তা করতে বসে বই নিয়ে। কেবল তাই না, লেখার এক ধরনের সিকোয়েন্স আছে, এক ধরনের রৈখিকতা আছে, যুক্তির একটা পরম্পরা বিন্যাস আছে, একটা অন্তর্গত ব্যাকরণ আছে। দেখা গেল অক্ষরহীন মানুষের সমাজ অতিক্রম করে আসা পড়ুয়া সমাজ লেখার যুক্তি ও পরম্পরার কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছে। সর্বোপরি, বইয়ের গড়নে একটা শুরু, মধ্য ও অন্ত থাকে— একটা পূর্ণতা আছে। আধুনিক মানুষও এইভাবে গুছিয়ে চিন্তা করতে শিখে নিয়েছে, একটা বিশেষ ছকে সে নিজেকে গড়ে নিতে চায়। পড়া ও লেখা আমাদের চৈতন্যের প্রবৃদ্ধি ঘটায়, প্রকৃতির সাথে বিযুক্তির ফলে আমাদের অন্তর্জগত আরও গভীর, সক্রিয় ও প্রসারিত হয়ে ওঠে। এক কথায়, লেখা ও পড়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ধরনকে যেমন নির্ধারণ করে দিয়েছে, এগিয়েও নিয়েছে। কথ্য বক্তব্য বা মুখের কথাকে লেখা এক ভিন্ন অনুভবের জগতে নিয়ে আসে, তা যে কেবলই মুখের কথার সহায়ক হয়ে থাকে এমন নয় বরং লেখা কন্ঠনিসৃত বক্তব্যকে কাগজের উপরে দেখার জগতে নিয়ে এসে বক্তব্যকেই আসলে বদলে দেয়, একইসাথে বদলে দেয় আমাদের চিন্তার ধরন। বলা যায়, ওরাল ট্র্যাডিশন বা কথ্য ঐতিহ্য অতিক্রম করে এসে চালু হওয়া স্বাক্ষরতা বা লেখা-পড়ার ঐতিহ্য, বিশেষত মূদ্রণের সহজলভ্যতা, আজ উদারনৈতিক আধুনিক সভ্যতা ও ভাবধারারই নামান্তর হয়ে উঠেছে।
৫. কিন্তু স্বাক্ষরতা বা লেখাপড়া এবং সেই সূত্রে গড়ে ওঠা উদারবাদী নীতিনৈতিকতা ও অভ্যাসের ঐতিহ্যও আজ এক প্রবল ঝুঁকির মুখে পড়েছে কিংবা অন্তুত এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে সে ঐতিহ্য আজ এক আমূল রূপান্তরের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে চলমান ভিজ্যুয়াল ও ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রবল উত্থানের ফলে। শিল্পবিপ্লবের পরে থেকেই প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি ঘটেছে। ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টার ইতিহাসও লম্বা। এবারে আমরা সে দেখনদারির অভ্যাস ও অভ্যস্ততা নিয়ে কিছু কথা বলব।
মানুষ ছবিমনষ্ক। মানুষের সংস্কৃতিও বলতে গেলে দৃশ্যের সংস্কৃতি। হোমোসেপিয়ান্সদের আদি গুহাগুলোতেও আমরা নানা রকমের আঁকাআঁকি দেখতে পাই। হয়ত যে শিকার তারা করে বা যে শিকার তারা করতে চায় সেগুলোকেই এঁকে যাদুটোনা করতে চাইত আরও ভালো শিকারের আশায়, হয়ত অন্য কিছুও আঁকত। পুজোর জন্যও অনেক ইমেজ তারা গড়ে তুলত। যেমন, নবী মুসা তুর পাহার থেকে ফিরে দেখতে পেলেন তার কওমের লোকজন এক স্বর্ণগাভি তৈরি করে তার পূজা করতে শুরু করেছে। আর প্রতিটি কৌমের নিজস্ব টোটেম তো ছিলই। ছবি ও ইমেজের প্রতি মানুষের আগ্রহ আদিম, এবং ইমেজ তার শরীরী অভিজ্ঞতারই অংশ। স্বাক্ষর-উত্তর এ সমাজে আজ হয়ত আমরা আবার সেখানে গিয়েই পৌঁছাতে শুরু করেছি। তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন মনে করতেন, ‘আমাদের মনের ভিতরের ইমেজই কেবল পারে আমাদেরকে প্রণোদনা জোগাতে’। আর সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনে করতেন, আমাদের অচেতন সত্তা গড়েই ওঠে ইমেজ দিয়ে।
তা সে যাই হোক, ছবি তোলা, সংরক্ষণ, দেখা, দেখানো ও বিতরণের প্রযুক্তি গড়ে উঠতে বহু শত বছর লেগে গেছে। সে বিস্তারিত আলাপে যাচ্ছি না। ১৯০০ সালেই মানুষ ছবি তোলার প্রযুক্তি আয়ত্ব করে ফেলে। সিনেমা দেখার জন্য প্রেক্ষাগ্রহ গড়ে ওঠে, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে থেকে টেলিভিশন। দৃশ্যরূপে মানুষের অধিকার ছিল কেবল ওই সম্প্রচারটুকুই। সাধারণ জনগণের সে প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রায় একেবারে ছিল না। তারা ছিল কেবলই রুটিন ভোক্তা। এদিকে, ভিডিও তৈরির প্রযুক্তি ১৯৩০-এর দশকে যাত্রা করলেও তা ছিল অত্যন্ত জটিল তো বটেই, অত্যন্ত ব্যয়বহুলও। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকে এসে আমরা একটা বড় রূপান্তর দেখতে পাই। ডিভিক্যাম মধ্যবিত্তের নাগালে চলে আসে, ডিভিডিতে রেকর্ড করার ও একইসাথে বিভিন্ন ডিভাইসে দেখারও সুযোগ তৈরি হয়। বলতে গেলে ডিভিক্যাম মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠে— এমেচার ভিডিও ও হোম ভিডিও তৈরির ধুম পড়ে যায়। ১৯৮০-এর দশক থেকে বাংলাদেশেও ডিভিডির রমরমা ব্যবসার কথা আমরা নিশ্চয় ভুলে যাইনি! ধর্মীয় কালচারের জগতে দেলোয়ার হোসেন সাইদী এবং গানের জগতে মমতাজ বেগমের উত্থান ঘটেছিল, অডিও ক্যাসেট আর ভিডিওর সুবাদেই।
আরও বড় রূপান্তর আমরা দেখতে পাই ১৯৯০-এর দশকে। এ সময়ে কেবল ভিডিও নির্মাণই সহজলভ্য হয়নি, ডিজিটাল ফরম্যাট আর নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তির সুবাদে ইন্টারনেটের কোনও সাইটে ভিডিও আপলোড করা, বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ার করাও সহজ হয়ে ওঠে। মোবইল ফোনে ক্যামেরা সংযুক্ত হয় ২০০০ সালে, ভিডিও ক্যামেরা ২০০৪ সালে। আর এখন তো সকল স্মার্টফোনেই স্থিরচিত্র ও ভিডিও চিত্র ধারণের বিপুল সুবিধা আছে। যে ভিডিও প্রযুক্তি এতোকাল কেবল পেশাদারদের অধিকারে ছিল তা চলে এল সর্বসাধারণের নাগালে, তাদের পকেটে।
কেবল কি তাই, আজকাল মোবাইলগুলো, ট্যাবগুলো, কম্পিউটারগুলো ইন্টারনেটের বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে যুক্ত। ২০০৭ সালে যাত্রা শুরু করে ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট নিয়ে সবচে বড় ওটিটি প্লটফর্ম ইউটিউব। তারপরে তো আরও কতো সামাজিক মাধ্যম এসেছে— যেখানে বিচিত্র ভিডিওর ছড়াছড়ি। দেখতেও পারেন, দেখাতেও পারেন। ফলে যেকোনো মুহূর্তেই আপনি, কেবল ভোক্তা নন, একজন নির্মাতা ও প্রডিউসার হিসেবেও হাজির হতে পারেন! ওয়াল্টার বেঞ্জামিন ১৯৩০-এর দশকে ফিল্মের পুনরুৎপাদনের সামর্থ্য দেখে খুব আশাবাদী হয়েছিলেন যে শিল্পবস্তুতে মানুষের অংশগ্রহণ বেড়ে যাবে, এর মধ্যে রয়েছে মানুষের মুক্তিদায়ী এক সম্ভাবনা। সে কথা একদিক থেকে সত্যও বটে। কিন্তু তিনি তো আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের কারিশমা দেখে যাননি! ভিডিও বানাতেও আজকাল আর লোক লাগে না! কিছু নির্দেশনার ভিত্তিতে ক্যামেরা বাদেই কম্পিউটার নিজে নিজেই ছবি ও ভিডিও বানাতে পারে, যা কোনওভাবেই অরিজিনাল থেকে আলাদা করাও যায় না। কম্পিউটার নিজেই এমন এক প্রযুক্তি যার তুলনা এ জগতে নাই, এবং তা এমন উপায়ে কাজ করে যা আমাদের চোখের অন্তরালে থেকে যায়! এমনকি আমরা দেখেছি, এক ভেড়ার জিন থেকে ক্লোন তৈরিও করা যাচ্ছে। যা কিনা জীবন্ত সত্তার কপি! ফলে, কোন সময়ে এসে আমরা দাঁড়ালাম! গত ৪০০ বছর ধরে স্বাক্ষরতা ও পড়ালেখাভিত্তিক যে উদারনৈতিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার কি হবে!
৬. সেই ১৯৬২ সালে ‘গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি’ বইয়ে মার্শাল ম্যাকলুহান ‘পোস্ট-লিটারেট সোসাইটি’ বা ‘স্বাক্ষর-উত্তর সমাজ’ ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। এ সমাজে বইপড়া-লেখা ইত্যাদি থাকবে না এমন কথা তিনি বলছিলেন না। বরং তিনি বলতে চেয়েছিলেন লেখাপড়া বা লেখা ও পড়ার সামর্থ্য আর এ সমাজের মুখ্য বিবেচনার বিষয় থাকবে না। এ বইয়ে তিনি সমাজকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন, স্বাক্ষরহীন বা কথ্যসমাজ, শিক্ষা বা লেখাপড়ার সমাজ, এবং স্বাক্ষর-উত্তর সমাজ। লেখা এবং পরবর্তীতে গুটেনবার্গের মূদ্রণযন্ত্রর প্রভাব স্বাক্ষরহীন বা কথ্যসমাজ অতিক্রম করে ইতিহাসভিত্তক এক শিক্ষা ও পড়ালেখার সমাজ কায়েম করেছিল। উদারনৈতিক ভাবাদর্শ তারই নিদর্শন। কিন্তু টেলিভিশনের চর্চা দেখে তিনি অনুমান করেছিলেন আমরা স্বাক্ষর-উত্তর সমাজে প্রবেশ করছি। তিনি মনে করতেন, টেলিভিশন কেবল ড্রয়িং রুমের একটা দেখার বস্তু না, বরং এমন এক প্রযুক্তি যা লেখা ও মূদ্রণের সংস্কৃতিকে আমূল বদলে দেবে। তিনি এই নতুন মানুষের নাম দিয়েছিলেন, ‘ম্যাস ম্যান’।
তিনি ভাবতেন প্রযুক্তির বিন্যাসের সাথে আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের ভারসাম্যেরও একটা ব্যাপার জড়িত। তিনি মনে করতেন স্বাক্ষরহীন বা কথ্যসমাজে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর ভারসাম্য ছিল। কিন্তু আধুনিক সমাজে লেখা ও পড়া আমাদের দেখার ইন্দ্রিয় চোখকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে, ফলে ইন্দ্রিয়ের ভারসাম্য নষ্ট হয়। অন্যদিকে, টেলিভিশন অনেক বেশি ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে, ফলে তা ইন্দ্রিয়ের ভারসাম্য অনেকটা ফিরিয়ে আনে। টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা স্বাক্ষর-উত্তর সমাজে পৌঁছে যাব। মূদ্রণভিত্তিক সমাজের যে ধীরগতি ও ছন্দ এবং রৈখিকতা টেলিভিশনের উপস্থাপনা তা ভেঙে দেয়। টেলিভিশন যেমন ইন্দ্রিয়ের ভারসাম্য আনে, তেমনই তার ইমেজের গতি, প্রবাহ, ধারাক্রম, এমনই যে স্বাক্ষরহীন বা কথ্য সমাজের সাথে তা মিলে যায়, যেখানে আবারও ম্যজিক ও মিথের আধিপত্য তৈরি হবে! প্রযুক্তির কল্যাণেই তা ঘটবে।
ম্যাকলুহানের এসব প্রাযুক্তিক নিমিত্তবাদী ধারণার সাথে একমত না হলেও, আজ এটুকু আমরা বলতে পারি, সর্বব্যাপী বা সর্বগ্রাসী ডিজিটাল প্রযুক্তি ও নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তির সুবাদে আজ আমরা এক নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। হয়তো ম্যাকলুহানের ‘ম্যাস ম্যান’ না বরং এ মানুষের সামান্যীকরণ করা চলে ‘এলগরিদমিক ম্যান’। যেমন ধারা যাক, বইয়ের একটা ভূমিকা বা শুরু, যুক্তির বিস্তার ও উপসংহার থাকে, সিনেমাতেও তাই। কিন্তু ইউটিউবে যান কিংবা ফেইসবুকের নিউজফিডে বা ভিডিও রিলে, দেখবেন সেখানে শুরু বা শেষ বলে কিছু নাই— কেবলই একটা লম্বা সারির মাঝখানে আপনি। ছোট ছোট ভিডিও রিল বা টিকটকে যান, দেখবেন সেগুলো আগের যুগের মতো কোনো একটা গল্প বলে না, কেবলই একটা মুহূর্তের অনুভব দিয়ে হারিয়ে যায়। দেখবেন, বৈচিত্রময় মুডের বিচিত্র রকম ভিডিওর সমাবেশ। আগের যুগের রাজনৈতিক স্লোগানের কথাই ভাবুন, তার একটা আদর্শ থাকত, একটা লক্ষ্য থাকত। অথচ আজকের যুগের ‘ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটারস’ কিংবা আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতার ‘খেলা হবে’ স্লোগানে কোনো স্থায়ী রাজনৈতিক এজেন্ডা নাই! আমরা এখন একটা তাৎক্ষণিকতার সময়ে বাস করছি, আর সে সময়ে ভিডিও আমাদের জীবনের এবং জীবনদর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। ভিডিওর মাধ্যমে যে অনেকে অনেক কিছু শিখছে না এমন নয়।
সময় বদলে যাচ্ছে। ফিরিবার পথ নাই, বরং এই সময়ের সাথে, যখন জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ নেটিজেন হয়ে উঠেছে, তারা ভিজুয়াল ও ভিডিওর জগতে সময় কাটায়। নতুন এই জনসমাজের সাথে আমরা কিভাবে মানিয়ে নিতে পারি, সমাজের সংহতি রক্ষা করতে পারি তা নিয়েই এবার ভাবতে বসা দরকার।
লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও লেখক।
ইমেইল: abdullahmamun@ru.ac.bd