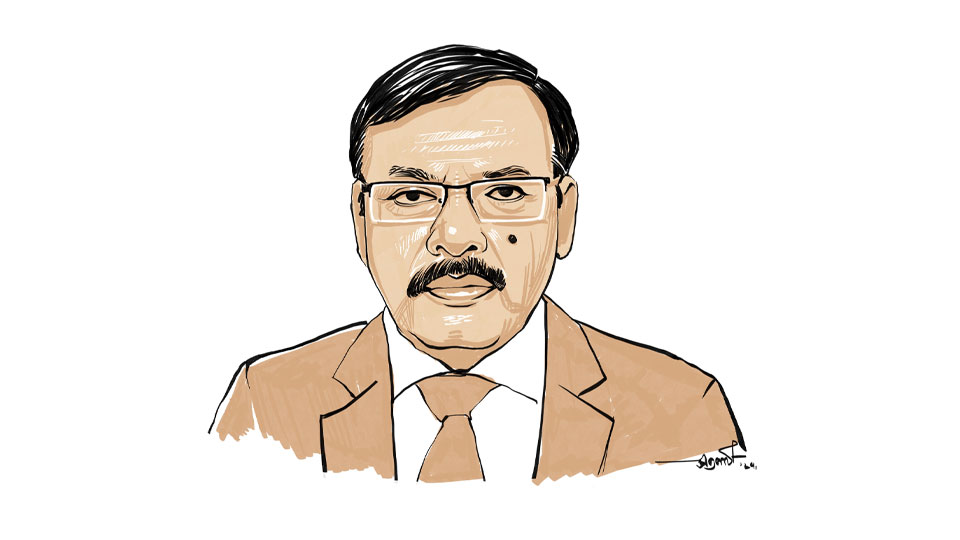নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত সে বইটি এখনও ঢাকার বৃক্ষচর্চার আকরগ্রন্থ। তিনি শ্যামলী নিসর্গ লিখে রেখে না গেলে সেকালের ঢাকার পথতরুর বৃত্তান্ত আমরা হয়ত জানতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকার সেসব পথতরুর এখন কী অবস্থা? আজও কি সেগুলো বেঁচে আছে? দ্বিজেন শর্মার আত্মজ সে বৃক্ষরা এখন ঢাকার কোথায় কীভাবে আছে সে কৌতুহল মেটানো আর একালের পাঠকদের সঙ্গে ঢাকার সেসব গাছপালা ও প্রকৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে এই লেখা। কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সরেজমিন অনুসন্ধানে তুলে ধরছেন ঢাকার শ্যামলী নিসর্গের সেকাল একাল। ঢাকার প্রাচীন, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য পথতরুর বৃত্তান্ত নিয়ে সকাল সন্ধ্যার পাঠকদের জন্য বাংলা বারো মাসে বারো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পড়ুন বৈশাখ পর্ব।
শত বছর আগেও ঢাকার রমনা এলাকা ছিল রম্য— প্রচুর গাছগাছালিতে ভরা। রমনা উদ্যানকে বলা হয় ঢাকা শহরের ফুসফুস— অক্সিজেন তৈরির কারখানা। এজন্য একে কেউ কেউ ‘রমনা গ্রিন’ বলেও ডাকেন।
এই এলাকার রমনা নামকরণ ঠিক কবে হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে জানা যায় না। তবে, মুঘল আমল থেকেই যে এই এলাকায় সমৃদ্ধ বাগান ছিল তার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায় একসময় এই এলাকার বাগানকে বলা হতো ‘বাগ-ই-বাদশাহী’ যা আধুনিককালে ‘শাহবাগ’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: ফাল্গুন পর্ব
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: চৈত্র পর্ব
তবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর রমনা ধীরে ধীরে তার পুরানো গৌরব হারিয়ে ফেলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে সরকারি কাগজপত্রে রমনার নাম তেমন একটা চোখে পড়ে না। বস্তুতপক্ষে সে সময় রমনা ছিল একটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত এলাকা যেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানকোঠা, মন্দির, সমাধি ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।
১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ব্রিটিশ কালেক্টর মি. ডয়েস ঢাকা নগরীর উন্নয়নকল্পে কতগুলি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই এই এলাকা আবার তার পুরানো গৌরব ফিরে পেতে শুরু করে। ওই সময় কালেক্টর ডয়েস কালী মন্দির ছাড়া অন্যান্য বেশির ভাগ পুরানো স্থাপনা সরিয়ে ফেলেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে রমনাকে একটি পরিচ্ছন্ন এলাকার রূপ দেন। পুরানো হাইকোর্ট ভবনের পশ্চিমে বর্তমানে অবস্থিত মসজিদ এবং সমাধিগুলি তিনি অক্ষত রাখেন।
পুরো এলাকাটি পরিষ্কার করে তিনি এর নাম দেন ‘রমনা গ্রিন’ এবং এলাকাটিকে রেসকোর্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেন। এই রেসকোর্স ময়দানই আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এ মাঠেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।
এই রমনা উদ্যানের বিশিষ্টতা বৈশাখে আমাদের অন্যভাবে উদ্দীপ্ত করে। রমনা উদ্যানের ভেতরে লেকের পাড়ে থাকা একটি গাছের তলায় বৈশাখের আহ্বানে বসে বাংলা নববর্ষের গানের আসর। সে সুর রমনার বটমূল (অশ্বত্থমূল) থেকে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বৈশাখ আর বট— এ যেন তখন হয়ে ওঠে বাঙালির আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু।
নবপত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে বট, অশ্বত্থ ও পাকুড়ের মতো পুরনো বছরের পাতা ঝরার গান—
ক্লেদ ও ক্লান্তি ঝরিয়ে নতুন বছরে বট-অশ্বত্থের নতুন পাতার মতো শুরু হয় বাঙালির নতুন জীবন।
সেই বৈশাখকে আলোকিত করে দেয় রক্তরাঙা কৃষ্ণচূড়া ও পালাম ফুল, সিঁদুররাঙা রক্তরাগ, গোলাপি সাদা নাগলিঙ্গম, শুভ্রসাদা কুরচি, সোনারঙা কনকচূড়া। বৈশাখে শোভিত বিরল ব্ল্যাকবিনের কমলা ফুলগুলোও যোগ করে নতুন মাত্রা। ঢাকা শহরে বৈশাখের দিনগুলোর এ এক অনির্বচনীয় নৈসর্গিক শোভা— প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য।
বাঙালির বট
মধ্যযুগের পালি ভাষার এক কবি বট নিয়ে লিখেছেন, ‘‘কুপোদকং বটচ্ছায়ায় শ্যামাস্ত্রী ইষ্টকালয়ম / শীতকালে তাবৎ উষ্ণা গ্রীষ্মকালে তু শীতলা।’’ অর্থ হলো— ‘‘কুয়োর জল, বটগাছের তলা, শ্যামলা স্ত্রী আর পাকা বাড়ি— এদের সান্নিধ্যে শীতকালে গরম থাকে এবং গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকে।’’ চৈত্রের দাবদাহ থেকে বৈশাখী ঝড়ো বাতাসের শীতলতা পেতে অনেকেই ছুটে আসেন বটছায়াতলে। রমনার বটমূল প্রতি বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছায়ানটের বর্ষবরণের গানের জন্য।
চৈত্রের ধুলি উড়িয়ে শুকনো ঝরাপাতা মাড়িয়ে আসে গ্রীষ্মের উদাসী হওয়া, কালবৈশাখীর প্রমত্ত উল্লাস। অশান্ত হাওয়ায় হয়তো মটামট ভাঙে দু’চারটি গাছের ডাল— ছিন্নভিন্ন হয় পত্রপল্লব, ফুলের কুঁড়ি, ফুল, কচি আম। কিন্তু সেই মহাতাণ্ডবের মধ্যে ধরণী ফিরে পায় নিঃসীম আকাশের সুধারস, সিক্ত হয় বসুন্ধরা।
বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির কোলে গাছগুলো আবার ফিরে পায় নতুন জীবনীশক্তি। সেই মহামন্ত্র আবাহনের অপেক্ষায় থাকে রমনা উদ্যান— উদ্যানের মহীরুহ বট আর অশ্বত্থগাছগুলো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোসহ গণমাধ্যম কর্মীদের মাধ্যমে ছায়ানটের শিল্পীদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত সেই মহাসঙ্গীতের সুর ছড়িয়ে যায় সবখানে। মহামতি গৌতম বুদ্ধ অশ্বত্থ গাছের তলায় বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। সে কারণে অশ্বত্থগাছ বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের কাছে এক মহাপবিত্র বৃক্ষ।
রমনা পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে লেকের পাড়ে রয়েছে বিখ্যাত ‘রমনার বটমূল’। সেই ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে (অশ্বত্থমূল) ছায়ানট বর্ষবরণের গান করে আসছে। এ কারণে রমনা উদ্যানের সে স্থানটি বিশ্বব্যাপী আলাদাভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সে আঙ্গিনায় লেকের পূর্বপাড়ে একটা বয়স্ক অশ্বত্থগাছ (Ficus religiosa) আছে।
অশ্বত্থ গাছের পাতা পানপাতার মতো, পাতার অগ্রভাগ সূঁচালো ও লেজের মতো বর্ধিত অঙ্গবিশিষ্ট। গাছে ঝুড়ি নামেনি। ঠিক এর উল্টোদিকে দক্ষিণে আর একটা বয়সী বটগাছ (Ficus benghalensis) আছে যার ঝুরি নেমেছে, আর পাতাগুলো পান পাতার মতো না, অনেকটা ডিম্বাকার, চামড়ার মতো পুরু, অগ্রভাগ ভোঁতা। ডালপালাসহ পৃথিবীর বৃহত্তম আকারের বিস্তৃত গাছ হচ্ছে বট, যার ডালপালার বিস্তৃতি দুই হাজার ফুট পর্যন্ত হতে পারে, যা ৫০০ থেকে ৬০০ একর জমির উপর ছড়িয়ে থাকতে পারে। ২০ হাজার লোকের সমাগম হতে পারে একটি বটগাছের তলায়।
ইতিহাস বলে, আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি নাকি এক লাখ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে ভারতের উত্তরপ্রদেশের এক বটগাছ তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই মহাবনস্পতি যুগে যুগে আমাদের বাঁচিয়েছে বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্বিপাক থেকে। অতীতে প্রায় সব হাটবাজার আর গ্রামের মধ্যে অন্তত একটা করে বটগাছ লাগানো হতো। কোনও কোনও গ্রামে সেই মহাবনস্পতির বিশালত্বে বিস্মিত হয়ে তাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হতো, সেসব গাছের তলা ‘মায়ের থান’ বলে পরিচিত হয়ে উঠত।

কীভাবে কখন এরূপ ধর্মাচারের শুরু— এ বিষয়ে তেমন একটা জানা যায় না। তবে এর পিছনে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য লুকানো, তা হলো গাছটিকে দুর্বৃত্ত বা ধ্বংসকারীদের হাত থেকে বাঁচানো। হিন্দু ধর্মে বটগাছের কাঠ পোড়ানো নিষেধ, সেটিও বটকে রক্ষার জন্য করা হয়েছে। যেন সে গাছ শতবর্ষ ধরে বিশাল থেকে বিশালকার রূপ ধরে ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে গ্রামবাসীকে বাঁচাতে পারে।
ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুরে দেখেছি বট ও পাকুড়ের বিয়ের প্রচলন। এক গ্রামের বট, অন্য গ্রামের পাকুড়। একত্রে এক জায়গায় লাগিয়ে তাদের বিয়ে দেওয়া হয় হিন্দু বিয়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনেই। মহা ধুমধামের সে দিনে বট হয় বরপক্ষ, পাকুড় হয় কনে পক্ষ। এর পেছনেও রয়েছে আর এক মহৎ উদ্দেশ্য। দুই গ্রামের গ্রামবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।




আজ এসব মিথ ও সামাজিকতা থেকে আমরা অনেকটাই সরে এসেছি। একটা গাছ এতটা জমি নষ্ট করে অযথা দাঁড়িয়ে থাকুক, তা এখন অনেকেই চান না। ঢাকা শহরে তো মোটেই নয়। বট একান্তই আমাদের আপন গাছ— বাঙালির বটগাছ। তবু বাঙালিদের কাছেই যেন বট এখন বিপন্ন।
বাঙালির বটগাছ বলেই হয়তো তার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের শেষে যোগ হয়েছে ‘বেঙ্গালেনসিস’ নামটা। এজন্য এ প্রজাতির বটের আর এক নাম ‘বাংলা বট’। বটের এরূপ আরও অনেক প্রজাতির গাছ এ দেশে দেখা যায়। এ দেশে যেসব বটগাছ দেখা যায় সেগুলো হলো— কাঁঠাল বট, আম বট, কানি বট, বট বা বাংলা বট, রাবার বট বা বড় বট, রিমা বট, লেজী বট, জিরবট, কামরূপ বট, ঝুলা বট, করাত বট, তোসা বট, সিলেটী বট, নাটা বট ইত্যাদি। আবার অশ্বত্থকে কেউ কেউ বলেন পানবট।

বট সত্যিই এক বিস্ময়কর বৃক্ষ যার ফুল কেউ কখনো চোখে দেখতে পায় না, এজন্য বোটানির ভাষায় এ ধরনের ফুলকে বলে অন্তঃপুষ্পী। ফলের মতো অঙ্গের মধ্যেই ফুলের বিকাশ ও ফলের ভেতরে ক্ষুদ্র বীজের জন্ম। তবে সেসব বীজ সংগ্রহ করে মানুষ নার্সারিতে তার চারা তৈরি করতে পারে না। প্রকৃতির এ এক অবাক রহস্য। কাক, শালিক, হরিয়ালের মতো কিছু পাখি লাল টুকটুকে সুগোল পাকা ফল খায়। পাখিদের পেটের ভেতরে সেসব বীজ জারিত হয়।
পাখি বিষ্ঠা ত্যাগের পর সেখান থেকে বটের চারা গজায়, তা সে মাটি বা ছাদের কার্নিশ যেখানেই হোক। এমনকি অন্য গাছের পুরনো ডালের উপরেও বটের চারা জন্মাতে অসুবিধা নেই। পাখিরা এ দেশ থেকে সে অন্য দেশে উড়ে যায়। আর বাঙালি বটগাছ এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে। যত দেশে, যত দূরেই যাই, কবি জীবনানন্দ দাশের মতো বটকে নিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—
‘‘একদিন জলসিঁড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নীচে শুয়ে রব: পশমের মত লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে।’’
বট ও অশ্বত্থের পর এবার আসা যাক পাকুড়ের কথায়। জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে আছে এক অচিন বৃক্ষ। প্রায় ১৫ বছর আগে ওই গাছটার গোড়ায় একটা নামফলক লাগানো দেখেছিলাম, তাতে লেখা ছিল— ‘অচিনবৃক্ষ’। কুড়িগ্রামের তৎকালীন জনৈক সংসদ সদস্য ওই গাছটি লাগিয়েছিলেন। কালক্রমে গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাকল বেড়েছে, মোটাসোটা হয়েছে আর ফলকটিও ঢাকা পড়ে গেছে। সে সময় আমিও সেই অচিনবৃক্ষকে শনাক্ত করতে পারিনি। তবে গাছের চেহারা দেখে বটগোত্রের কোনও গাছ বলেই মনে হয়েছিল। পরে দেখি পাকুড়।
চন্দ্রিমা উদ্যানের ভেতরেও পূর্ব দিকে রয়েছে আর একটি পাকুড় গাছ। বট আর পাকুড়ের মূল প্রভেদ হলো, বটের চেয়ে পাকুড়ের পাতা ছোট, ফলও ছোট— বটের ফল লাল, পাকুড়ের ফল সবুজাভ সাদা বা হলুদ। সারা বিশ্বে বটজাতীয় অর্থাৎ ফিকাসগণের প্রায় সাড়ে আটশ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে।
বট, অশ্বত্থের সঙ্গে পাকুড়ও ওদের স্বগোত্রীয় বৃক্ষ। মহুয়া, সফেদা, রাবার, বট, অশ্বত্থ ও পাকুড়কে বলা হয় ক্ষীরী বৃক্ষ। কেননা, এসব গাছের ডাল ও পাতা ভাঙলে সাদা দুধের মতো ঘন আঠা বের হয়, যাকে বোটানির ভাষায় বলা হয় তরুক্ষীর বা ল্যাটেক্স। পাকুড় গাছকে দেখেই হয়তো কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—
‘‘চৈত্র মাসে তাদের নীচে কত যে
শুকনো পাতা ঝরে পড়তো, হাওয়ায় সেগুলো
ঘুরে ঘুরে পাড়াময় যেতো ছড়িয়ে।
বৈশাখে তাদের নতুন রূপ, জটে বাঁধা প্রচণ্ড
ঝুনো শরীরে কচিপাতা ঠিক যেন মানাতো না।
হাওয়ার দিনে অশ্রান্ত অশ্রাস্ত মর্মর, …’’
দ্বিজেন শর্মা ঢাকা শহরে বটগাছের অবস্থান নির্দেশের জন্য অবশ্য বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে থাকা ঝুরি নামা সুদৃশ্য বটগাছটির কথাই বলেছেন, রমনা উদ্যানেরটা নয়। কেননা, রমনার বিখ্যাত গাছটি আসলে বটগাছ না— অশ্বত্থগাছ। বাংলা একাডেমির এ বটগাছের তলায় বৈশাখী মেলার ও অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করা হয়।
এছাড়াও দ্বিজেন শর্মা লিখেছিলেন, নিউমার্কেটের পশ্চিমে দু’সারি বটের শাখা-প্রশাখা জড়ানো সুড়ঙ্গকল্প এক আকর্ষীপথ ছিল যেটি এখন নেই— সড়ক উন্নয়নে কাটা পড়েছে। তবে সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত তার এক সাক্ষাৎকারে শুনিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঐতিহাসিক বটতলার কথা।

এখনকার যে বটগাছ, সেটা আমাদের স্বাধীনতার সমান বয়সী। কিন্তু তার আগে ওখানে যে বটগাছটা ছিল তার তলায় উঠানো হয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম পতাকা। এটাকে অপরাধ হিসেবে ধরে নিয়ে পাক সেনারা একাত্তরে সে গাছটা কেটে ফেলে বা কামান দেগে উড়িয়ে দেয়। বর্তমান বটগাছটি ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি লাগান তৎকালীন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি।
বটের একটি অন্তরঙ্গ প্রজাতি পাকুড় সম্পর্কে দ্বিজেন শর্মা ‘শ্যামলী নিসর্গে’ লিখেছেন, ‘‘পাকুড় বিশালতায় বটের যোগ্য আত্মীয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিকটস্থ শহীদ মিনার থেকে শুরু করে বক্সীবাজারের সিটি রোডের মুখ পর্যন্ত রাস্তার পাশে যে গাছের সারিটি একদিকে হেলে পড়েছে সে-ই পাকুড়।’’ তিনি পাকুড়ের বৈজ্ঞানিক নাম লিখেছেন ‘ফিকাস কোমজা’ যার ফল হলুদ। কিন্তু বইপত্র ঘেঁটে দেখলাম ওটা মোসা-ডুমুরের বৈজ্ঞানিক নাম, উদ্ভিদ অভিধানে পাকুড়ের বৈজ্ঞানিক নাম ‘ফিকাস বেঞ্জামিনা’।
আবার মোকারম হোসেন তার ‘বাংলাদেশের পুষ্প-বৃক্ষ লতা-গুল্ম’ বইয়ে পাকুড়ের বৈজ্ঞানিক নাম লিখেছেন ‘ফিকাস ভাইরেন্স’ যার ফলের রঙ কমলা। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর প্রকাশিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের গাছপালার তালিকায় পাকুড় হলো ‘ফিকাস লেকর’।
কাজেই বট আর অশ্বত্থ চেনা যতটা সহজ, পাকুড় চেনা তত সহজ না। বৈজ্ঞানিক নাম যাই-ই হোক শ্যামলী নিসর্গের পাকুড়গাছগুলোর অবস্থা দেখতে বৈশাখের এক সকালে গিয়ে হাজির হলাম শহীদ মিনারের কাছে। কয়েকটা সেই প্রাচীন পাকুড় গাছ বুড়ো শরীরে এখনও দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের গেটের পাশে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে।
কৃষ্ণচূড়া ও সোনালু ফোটার দিন
দ্বিজেন শর্মার এক বন্ধু ‘হালমার্কিন’ বইয়ের লেখক জহুরুল হক ঠিক ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এসেছিলেন ঢাকা শহরে চাকরিতে যোগ দিতে। বয়স তখন তার ৩০ বছর। চাকরির পাশাপাশি ঢাকার গাছপালাও ছিল তার অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এ নিয়ে মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার ‘বৃক্ষ ও পরিবেশ’ সংখ্যায় তিনি লিখেছেন ‘সুখে-দুঃখে আমি, ঢাকার গাছপালা’ শীর্ষক একটি নিবন্ধ।

সে নিবন্ধে সে সময়ের ঢাকা শহরের গাছপালার মোটামুটি একটি পরিচয় পাওয়া যায়, পরিচয় পাওয়া যায় ঢাকা শহরেরও। লিখেছেন, ‘‘স্টেডিয়াম ছিল না, নিউ মার্কেট ছিল না, সোহরাওয়ার্দি উদ্যান ছিল না, ওদিকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ছিল না, বঙ্গভবন তো ছিলই না, চিড়িয়াখানা কি জাদুঘর নয়, এমন উঁচু উঁচু বাড়ির বাণিজ্যিক এলাকাটাও ছিল না। ভালো সিনেমা হল কি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের কথা ছেড়েই দিলাম।’’
এত কিছু না থাকলেও ছিল সবুজ শ্যামলিমায় ভরা ঢাকা শহর। সেটির কথা জানা যায়— মার্কিন মুলুক থেকে সে সময় আসা জনৈক বিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাছে তিনি শুনতে চেয়েছিলেন যে, ঢাকা শহরকে তার কেমন লেগেছে? জবাব পাওয়া গিয়েছিল সেই বিদেশী যুবকের কাছ থেকে, ‘‘আর একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে: তাহলো এখানকার গাছপালা। এতো সুন্দর, আর এতো রকমের ফুল, কোথাও না কোথাও ফুল ফুটে আছেই, একটা শেষ হতে না হতেই আর এক রকমের ফুল এসে হাজির। রঙের এতো বিশাল সমারোহও আমি দেখিনি কোথাও এর আগে।’’
সেকালে ঢাকা শহরে গ্রীষ্মের যে প্রকৃতিশোভা জহুরুল হক দেখেছেন সেই নিবন্ধে তার বর্ণনা আছে— ‘‘বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢাকা শহরের এক এক অঞ্চলে সে কি ফুল ফোটানোর মাতামাতি! টকটকে লাল ফুল, হলদে-লাল ফুল, বেগুনী ফুল, হলদে ফুল, সাদার উপরে গোলাপী ফুল, সাদা ফুল। কত রঙ তার শেষ নেই। ঐ অঞ্চল ছিল কোন্টা? সোহ্রাওয়ার্দি উদ্যানের পাশের রাস্তার একধারে পাবলিক লাইব্রেরিও ছিল না, আর্ট কলেজ, মসজিদ, মাজার কিছুই ছিল না— ঘন করে লাগানো এক সার বড়ো বড়ো গাছ ছিল। ঐ সময় রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথায় ফুল দেখা যেত,- রঙের ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন। টকটকে লাল ফুলগুলো ছিল কৃষ্ণচূড়া।’’ আজ সেসব হারিয়ে গেছে।



তবে সেসব কৃষ্ণচূড়ারা যেন আজ আবার স্বরূপে ফিরে এসেছে জাতীয় সংসদ ভবনের উত্তর পাশে ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ের রাস্তায়। চন্দ্রিমা উদ্যানের ছোট্ট ঝিলের পাড়ে লাল ইট বিছানো ফুটপাতে সকালবেলায় বৈশাখের দিনগুলোতে ঝরে পড়ে লাল টুকটুক কৃষ্ণচূড়া (Delonix regia) ফুলেরা। নবীন তরুপল্লবের ফাঁকগুলো ভরে আছে থোকাধরা রক্তলাল ফুলে। এ রাস্তার নামটা ‘কৃষ্ণচূড়া সরণী’ হলে মন্দ হয় না। ঢাকা শহরে এ রাস্তার দু’পাশে যতগুলো কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে আর কোনও রাস্তায় এভাবে নেই।
বৈশাখ এলেই রাজরাণীর মতো ফুলের ডালি সাজিয়ে বসে গাছগুলো, পথিকদের চোখ তা দেখে আনন্দে মেতে ওঠে। গত বছর এক কালবৈশাখী ঝড়ের পর চন্দ্রিমা উদ্যানের ঝিল পেরিয়ে একটা বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখেছিলাম অন্য রূপে। বিশাল সে বয়সী বৃক্ষের পাদমূল চারদিকে কয়েকটা খাড়া দেয়ালের মতো ডানা মেলে দাঁড়িয়েছিল, তার তলায় দাঁড়িয়ে শুনছিলাম বিরহ বেদনের নীরব সঙ্গীত। কালবৈশাখী ঝড়ে এক সন্ধ্যায় তার ডালপালা ভেঙে, পত্রপল্লব খসিয়ে ফুলগুলো দুমড়ে মুচড়ে মাটির উপরে ছড়িয়ে ছিল। গাছের তলাটা ঢেকে ছিল লাল লাল পাঁপড়িতে— এমন ফুলশয্যা রচনার নেপথ্যে রয়েছে কৃষ্ণচূড়ার বিরহ সঙ্গীত।
যে ফুলকে শ্রীকৃষ্ণ ঠাঁই দিয়েছে তার মাথার চূড়ায়, যে ফুলের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সেই কৃষ্ণচূড়া ফুলেরই কি-না এত অবমাননা, অনাদর? সত্যিই তো, যে ফুল শোভা পায় শ্রীকৃষ্ণের কেশরে, সেই ফুল কেন পড়বে ধরণীর কুন্তলে, ঘাসের উপর কেন লুটোপুটি খাবে ফুলগুলো? কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এ ফুলের নামেই লিখেছিলেন তার ‘কৃষ্ণচূড়া’ কবিতা। ফুলময় সে কবিতার প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি এ ফুলের মর্যাদা দিতে ভোলেননি—
‘‘এই যে কুসুম শিরোপরে, পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল রতনে !
বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতুহলে
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী?’’
বৈশাখের প্রথম বৃষ্টিচ্ছটায় ফুলের পাঁপড়িগুলো ছিল সতেজ। সবুজ ঘাসের উপর ফুলগুলো বিছিয়ে ছিল চাদরের মতো। কৃষ্ণচূড়া সত্যিই এক অপূর্ব শোভাময়ী উদ্যানবৃক্ষ ও পথতরু। গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রকৃতিতে আগুন জ্বালানো ফুল। এ ফুল আমাদের খুবই পরিচিত, চিনতে ভুল হয় না, কিন্তু তারাপদ রায়ের হয়েছিল। তিনি তার ‘আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে’ কবিতায় এই বিভ্রান্তি প্রকাশ করেছিলেন রূপক অর্থে—
‘‘আমরা যে গাছটিকে কৃষ্ণচূড়া গাছ ভেবেছিলাম
যার উদ্দেশ্যে ধ্রুপদী বিন্যাসে কয়েক অনুচ্ছেদ প্রশস্তি লিখেছিলাম
গতকাল বলাই বাবু বললেন, ‘ঐটি বাঁদরলাঠি গাছ’।
অ্যালসেশিয়ান ভেবে যে সারমেয় শাবকটিকে
আমরা তিন মাস বক্লস পরিয়ে মাংস খাওয়ালাম
ক্রমশ তার খেঁকিভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।
আমরা টের পাইনি’’
কবিতার ওই বাঁদরলাঠি গাছগুলোরও দেখা পেলাম সংসদ ভবনের পূব ও পশ্চিম পাশের প্রবেশ পথের পাশে। ঝাড়বাতির মতো হলুদিয়া রূপের পসরা সাজিয়ে বসেছে ঘন কচি পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে। কাঁচা সোনার মতো রঙ আর ঝাড়বাতির মতো ঝুলানো ফুল বলেই এর আর এক নাম সোনাঝুরি— সোনারঙ ফুল বলে নাম সোনালু বা সোনাল (Cassia fistula)। গ্রীষ্মের শেষে লম্বা লাঠির মতো ফল ঝোলে, এজন্যই এর নাম বাঁদরলাঠি বা বান্দরলাঠি। বানররা এর পাকা ফলের শাঁস খেতে পছন্দ করে বলেই হয়তো এরূপ নাম। মানুষও ইচ্ছা করলে তেঁতুলের মতো পাকা ফলের মিষ্টি শাঁস খেতে পারে।


বিক্ষিপ্তভাবে এ গাছ লাগানো আছে রমনা পার্কের বিভিন্ন স্থানে। তবে জাতীয় সংসদ ভবনের পূর্বপাশের রাস্তায় আগে সোনাঝুরির যে বাহারি রূপ ছিল, তা মেট্রো রেলপথের জন্য কিছুটা আড়ালে পড়েছে। এ অংশেই খেজুর বাগানটার পিছনে লাগানো আছে কয়েকটা আরেক রকমের সোনালু গাছ। নাম তার লাল সোনালু (Cassia javanica)। নামটা লাল সোনালু হলেও ফুলগুলো লালাভ গোলাপি। থোকা ধরে ফুল ফোটে গ্রীষ্মকাল জুড়ে। ফুলের প্রাচুর্যে পুরো গ্রীষ্মকাল আলোকিত হয়ে ওঠে।
ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) প্রবেশপথের পাশে, চন্দ্রিমা উদ্যানের ভেতরে, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ও সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের প্রবেশ দ্বারেও রয়েছে এ গাছ। ধানমন্ডি ঝিলের পাড়েও সারি করে লাগানো কয়েকটা তরুণ লাল সোনালু চারাগাছ আছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সিএমএইচ প্রাঙ্গণে গোলাপী সোনালু (Cassia bakeriana) নামে কিছু গাছও আছে যার ফুল ফোটে বসন্তে, ফুলের রঙ মিষ্টি গোলাপি।

চারদিকে ছাতার মতো ছড়ানো ডাল-পাতার ছায়াতরু ও পথতরু হিসেবে অপূর্ব শোভাময়ী লাল সোনালু। এ গাছের লাল সোনালু নামটা দিয়েছিলেন নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা, ভারতীয় বাংলা নাম ‘লোকেশ্বর’। ফুল শেষে গাছে শিমের মতো ফল হয়, ফলের ভেতর শিমের বিচির মতো বীজ হয়। শুকনো ফল পেড়ে বীজ বের করে জলে এক রাত ভিজিয়ে মাটিতে পুঁতে দিলে সেখানেই এ গাছ হয়ে যায়। সোনালুরও তাই। বিচি থেকে গাছ হয় সহজে। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে কয়েক ডজন সোনালু গাছে বৈশাখে ফুলের স্ফুরণ বিমোহিত করে। গায়ে গায়ে সেখানেও বেড়ে উঠেছে কয়েকটা লাল সোনালু বা কেসিয়া গাছ।
চৈত্রের চাঁদর উড়িয়ে এসেছে বৈশাখের হাওয়া। বসন্তে ফোটা নাগকেশর ফুলরা ঝরে গেছে। বসন্ত-গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণে জেগে উঠেছে বেণীর মতো দোলানো সোনাঝুরির অজস্র কুঁড়ি। পৃথিবীর প্রকৃতির জাদুমঞ্চে এ যেন এক ঐন্দ্রজালিক পালাবদল। বিস্মিত হই এই ভেবে যে, পঞ্জিকা না দেখেও প্রকৃতির শোভা ও রূপ দেখে, ফুলের উপস্থিতি দেখেও বুঝতে পারি ঋতুচক্রের এই অপরূপ পালাবদল।
বিশ্বের আর কোনও দেশে ছয়টি ঋতুর এমন সমারোহ সত্যিই বিরল। বছরের প্রথম ঋতু গ্রীষ্মের অস্তিত্ব ঘোষণা করে কৃষ্ণচূড়া-সোনালু-জারুল, বর্ষা ঋতুর ঘোষণা দেয় কদম-মালতী ফুল, শরতের আগমন ঘটে শিউলি আর কাশফুলের কাঁধে চড়ে— পদ্মফুলের মাথায় ভ্রমররা খেলা করে, হেমন্তে ফোটে সুগন্ধি সোনাপাতি— রক্ত লাল শাপলা ফুল, শীতের জানান দেয় হলুদ গাঁদারা, ঋতুরাজ বসন্তে ফোটে চম্পা-কুরচি-নাগকেশর, আরও কত কি!
গ্রীষ্মের প্রথম মাস এলে হৃদয়ে বাজে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো— ‘‘পেরিয়েছ ফাল্গুনের ভাঙাভাণ্ড উচ্ছিষ্টের ভূমি, পৌঁছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে, … জ্যৈষ্ঠ-অবসানদিনে আকস্মিক জুঁই যেমন চমকি জেগে উঠে।’’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘নামকরণ’ কবিতায় লিখেছেন—
‘‘বসন্তে নাগকেশরের সুগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাদুর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।
বনতলে মর্মরিয়া কাঁপে সোনাঝুরি;
চাঁদের আলোর পথে খেলা করে ছায়ার চাতুরী;’’
কথা দিয়ে প্রকৃতির চিত্রকল্প তৈরির কি অদ্ভুত শক্তিই না কবিদের থাকে! চাঁদনী রাত, জোছনায় ভেসে যাচ্ছে প্রকৃতি— গাছপালা। বসন্ত বাতাস উদ্বেল ছিল নাগকেশরের মাতাল সুগন্ধে, তার অবসানে এসেছে সোনাঝুরির সঙ্গে চাঁদের চৈতন্যলোক— এমন চাঁদনী রাতে শিরায় শিরায় বেজে ওঠে সেতারের সুর, দেহে বুলিয়ে দেয় অনামীর অদৃশ্য উত্তরীয়। একই রকমের অনুভূতির আর এক চিত্রকল্প পাই কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানে—
‘‘নতুন চাঁদের জোছনা মাখি সোনাল শাখায় দোল দুলায়ে
কে এলে গো, কে এলে গো চপল পায়ে॥’’
নজরুল তার একটি গানে বৈশাখে ফোটা কৃষ্ণচূড়া আর সোনালু ফুলের এক যুগল চিত্রকল্প রচনা করেছেন, সেখানে প্রকৃতির শোভায় শুধু ফুল না— দোয়েল শ্যামা হলদে পাখিও এসেছে সে ফুলের রূপে—
‘‘দোয়েল শ্যামা লহর তোলে কৃষ্ণচূড়ার ফুলের শাখায়॥
বন-গোপিনী ফুল ছুঁড়ে ঐ খেলে হোলী দখিন-বায়ে,
হলদে পাখি দোদুল দুলে সোনাল শাখায় আদুল গায়ে।’’
কবি সুভদ্রা রায়ের ‘কৃষ্ণচূড়া’ কবিতাটির সন্ধান পাই অন্তর্জালে। কী চমৎকার করে যে তিনি এ ফুলের রূপ বর্ণনা করেছেন সেখানে—
‘‘গন্ধহীন এ ফুলের নামে মন্ত্র পড়েনি আজও পুরোহিত
দেবতার পায়ে হয়নি কো স্থান— জগৎ পিতা তোমায় নিয়ে মেতেছে বারবার
চূড়ায় পড়েছে কৃষ্ণ তোমায়— তোমারই জয়গান,
রুদ্র দাবদাহে তোমার ছায়াতলে ছত্র মেলেছে আকাশ জুড়ে
কত পশু পাখি পথিকের দীর্ঘশ্বাস তোমার শীতল ছায়ায় পায় প্রাণ— ভালবাসা নাম লেখে
প্রেমিক প্রেমিকার
আদিবাসী রমণীর সাজের অঙ্গ তুমি
প্রেয়সীর সুপ্ত কামনার বর্ণে রাঙা খোঁপাখানি—
গুচ্ছ গুচ্ছ শোভা পায় বেলা অবেলার দ্বারে
নানা রঙে তোমার সম্ভার আনি,
প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে বর্ণ তোমার
লাল কমলা গোলাপি বিরল হলুদেও আছো তাই
তোমার শাখায় বসে কপোত কপোতী ভাবে
এত প্রেম এত সুখ কেমনে আসে—’’
পাহাড়ি ফুল পালাম
‘রমনার বটমূলে’ অশ্বত্থ গাছের ঠিক উল্টোদিকে লাগানো আছে কুড়িটা পালাম গাছ, অন্য নাম পলান। রমনার নার্সারির মধ্যে কুরচি গাছের পাশে জোড় বেঁধে রয়েছে একটি দীর্ঘ বয়স্ক পালাম গাছ। মাটি থেকে গাছের মূল কাণ্ডে কোনও ডালপালা নেই, মাথায় ছাতার মতো অনেকগুলো ডাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি ডালের ঘন কালচে সবুজ পাতার মধ্যে অসংখ্য ফুল। যেন রাজতিলকের মতো শোভা পাচ্ছে।

গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তার শোভা দেখার চেষ্টা করলাম। গাছের তলায় কার্পেট ঘাসের সবুজ গালিচা। অসংখ্য ঝরা ফুলে তলাটা ভরে আছে। ফোটা ফুল থেকে গন্ধ ভেসে আসছে। গাছটির উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে ফুটে আছে কড়া লাল বা লালচে খয়েরি পাঁচ পাঁপড়ির অজস্র পালাম ফুল।

এ গাছ এ দেশে সুলভ নয়, পাহাড়ে জন্মে— সিলেটের পাহাড়ি বনে দেখা যায়। রমনা উদ্যান ছাড়া ঢাকা শহরে আর কোথাও পালাম গাছ চোখে পড়েনি। এমনকি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানেও পালাম নেই। ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়েও পালামের নাম উল্লেখ নেই। তাতে মনে হয় সিলেটের পাহাড়ি বন থেকে চারা সংগ্রহ করে কোনো একসময় তা রমনা উদ্যানে লাগানো হয়েছে।
পালাম দক্ষিণ এশিয়ার গাছ। বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, চীন, থাইল্যান্ডের পার্বত্য অরণ্যে এ গাছ দেখা যায়। পালামের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ‘Wrightia coccinea’ ও গোত্র অ্যাপোসাইনেসি। ইংরেজি নাম স্কারলেট রাইটিয়া। বাংলা নাম পালাম বা পলান। পালাম মাঝারি আকারের বৃক্ষ, চিরসবুজ ও ধীর বৃদ্ধি স্বভাবের।
এ গাছটি সাধারণত ২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। কাণ্ডের বাকল সাদাটে ধূসর থেকে বাদামি ধূসর, মসৃণ। পাতা উপবৃত্তাকার থেকে ডিম্বাকার। পাতার আগা সূঁচালো ও লম্বাটে। ডালের আগায় গ্রীষ্মের শুরুতে ফুল ফোটে। ফুল ফানেল আকৃতির, ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ি, রঙ ঘন লাল, ফুলের গন্ধে মাছি আকৃষ্ট হয় ও মাছিরাই এর পরাগায়ন ঘটায়। ফলগুলো লম্বা, কলচে সবুজ, সাদা ফুটি দাগে ভরা। ফলের ভেতরে বীজগুলোও লম্বা। বীজ থেকে চারা তৈরি করা যায়। সড়কের পাশে, পার্কে বা বাগানে শোভাময়ী এ গাছ লাগানো যায়।
পাহাড়ি ফল মাইলাম
পাহাড়ি ফল মাইলামের দেখা পেয়েছিলাম, প্রথমবারের মতো প্রায় ২০ বছর আগে এক বৈশাখের দিনে টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার পথে। ঝুড়িতে করে ফেরিওয়ালা ফল বিক্রি করছিলেন। পাকা ফলগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল বড় কুলের মতো। ফেরিওয়ালাকে ফলের নাম জিজ্ঞেস করতে তিনি বলেছিলেন, ‘‘বুনা আম। নাফ নদীর ধারে পাহাড়ে অনেক গাছ আছে, সেখান থেকে আমরা পেড়ে আনি। গরমের মধ্যে এই ফল খাইলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।’’
একটা খেয়ে দেখলাম। ভীষণ টক, আর আঁটি বড়, আঁশে ভরা। মনে হলো এটি আমের হয়তো কোনও দাদী-নানী হবে। কেননা, আমের জন্মস্থল হলো মিয়ানমার ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল। সে হিসেবে আমের এর রকম অনেক প্রজাতির গাছ এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বৃক্ষবন্ধু বেণুবর্ণা অধিকারী বললেন, ‘‘রমনায় মাইলাম গাছের তলায় বৈশাখের দিনে গাছ থেকে ঝরে পড়া মাইলাম ফল খেতে কি যে মজা!’’

অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অবশেষে বৈশাখ এলো, রমনার উত্তরায়ন ফটক দিয়ে প্রবেশ করে একটু এগিয়ে গোলাম। শৌচাগারের দু’পাশে দুটো বিরাট প্রাচীন মাইলাম গাছ। গাছ দুটোকে দেখে রমনার স্থপতি প্রাউডলকের কথা মনে পড়ল। তিনি একই সঙ্গে রেঙ্গুন ও ঢাকায় উদ্যান তৈরির দায়িত্ব পেয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে। তিনি হয়তো মিয়ানমার থেকে এই মাইলামের চারাগুলো এনে রমনায় লাগিয়েছিলেন। সেই গাছ এখন মহীরুহ ও ঢাকায় মাইলামের একমাত্র প্রতিনিধি।
বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর থেকে ২০২১ সালে প্রকাশিত ‘ফ্লোরা, ফনা অ্যান্ড ইকোলজি অব বাংলাদেশ ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন’ গ্রন্থে ঢাকার মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ১০৪২ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে বলে একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সে তালিকাতেও নেই মাইলাম।
জানা মতে, বিশ্বে আমের প্রজাতির সংখ্যা ৬৯টি। এর মধ্যে বাংলাদেশে আছে আম (Mangifera indica), মাইলাম বা জংলি আম (Mangifera longipes) ও লক্ষী আম বা বন আম (Mangifera sylvatica)। মাইলাম মালি আম, মাউজ্জাম বা মুহিঞ্জি নামেও পরিচিত। মাইলাম সাধারণত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের বনে জন্মে।


রমনা পার্কের মধ্যে বেশ কয়েকটা মাইলাম গাছ আছে। গাছটি দেখতে বড় বৃক্ষের মতো— চিরসবুজ। পাতা ও ফল আমের মতো হলেও আকারে সাধারণ আমের চেয়ে অনেক ছোট, পাতা কালচে সবুজ ও ঘন। অগ্রহায়ণে মুকুল আসে, চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখে ফল পাকে।
আমের মতো এর মুকুল খাড়া হয় না, নিচের দিকে ঝুলানো থাকে। এ দেশে যত প্রজাতির ও যত জাতের আম আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আগে পাকে এই আম। কাঁচা আমের রঙ সবুজ, পাকলে হয়ে যায় ঘোলাটে হলুদ, আকারে দেশি মুরগির ডিমের চেয়েও ছোট, ডিম্বাকার, খোসা পুরু, পাকা আম রসাল, স্বাদে টক।
ইন্দোনেশিয়ান জার্নাল অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ২০২১ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যার এক গবেষণা নিবন্ধে মাইলামকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘ডায়াবেটিক আম’ হিসেবে। এমনকি এ গাছের পাতা ডায়াবেটিস, ম্যালেরিয়া, যকৃৎ ও আন্ত্রিক সমস্যা এবং ক্ষত সারানোয় উপকার করে বলে সে নিবন্ধে লিখেছেন গবেষকবৃন্দ— নূর, পিরান্তি ও দিয়ানা।
নরকের খুব কাছে আছি
ঢাকা শহরের চারদিকে তাকিয়ে মনটা বেদনায় ভরে ওঠে, বিষণ্ন চোখে তাকিয়ে তথাকথিত উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে যায় আমার সবুজ স্বপ্নগুলো। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি, ধুলিধূসর পুঁতিগন্ধময় পাখির ডাকবিহীন এক বিপর্যস্ত নগরকে যেখানে মানুষ আছে, মানুষের মন নেই, প্রকৃতি আছে কিন্তু প্রকৃতির প্রাণ নেই।
এখানে গাছগুলো যতই মানুষের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করে, মানুষ যেন ততটাই গাছের শত্রু হয়ে ওঠে। যে গাছ দেয় আমাদের শ্বাসের জন্য জীবনপ্রদায়ী অক্সিজেন— জীবনের জ্বালানি, সেই গাছই উন্নয়নের আগুনে দগ্ধ হয়ে হয়ে যাচ্ছে, পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে— অক্সিজেনের বদলে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনবিনাশী বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড।
ঢাকা শহরে গাছদের কথা ভাবলে খুব খারাপ লাগে। পাখিদের ওপর অত্যাচার করলে তারা পালিয়ে বাঁচতে পারে আকাশে উড়ে গিয়ে। গাছেরা পালাবে কোথায়? ওরা তো উড়তে পারে না, হাঁটতেও পারে না। কষ্ট পেলেও চিৎকার করে কাঁদতে পারে না। ওদের সেসব চাপা কষ্ট যেন আজ আমাদের জন্য অভিশাপ হয়ে আসছে।
মাঝে মাঝে স্বপ্নে যেন গাছেদের সঙ্গে আমার কথা হয়। নিঝুম নিশুতি রাতে ফিসফিস করে গাছেরা বলে— দুঃখিত বন্ধু, তোমাকে আমরা আর রক্ষা করতে পারলাম না। আমাদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে, আমরা ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছি।
মৃত্যুর পর সারা জীবন তোমাদের উপকারের জন্য বিধাতা আমাদের স্বর্গের উদ্যানে নিয়ে যাচ্ছেন—
যে স্বর্গ থেকে একদিন তিনি আমাদের এই মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন। আর তোমরা, তোমাদের জন্য বিধাতা নরকের দরজা খুলে বসে আছেন। সে নরকের খুব কাছে চলে এসেছো তোমরা। সাধ্য কি আছে ফেরার?
লেখক: কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক।
ইমেইল: kbdmrityun@gmail.com